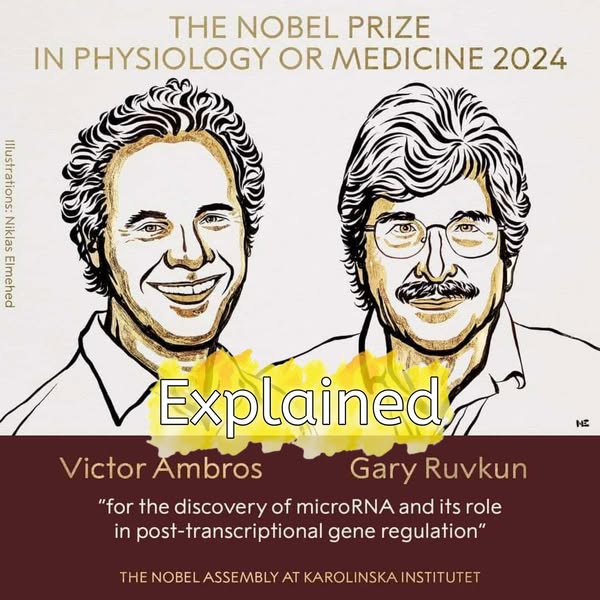মানুষের কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত জোড়া? এর উত্তর কমবেশি আমরা সবাই জানি। প্রতি কোষেই ২৩ জোড়া করে ক্রোমোজোম আছে এবং সকল ক্রোমোজোমে রয়েছে ঠিক একইরকম জিন, একইরকম তথ্য উপাত্ত। এই তথ্যই আমাদের সকল বাহ্যিক (দৈহিক এবং মনস্তাত্ত্বিক) বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোমোজোমে থাকা ডিএনএ তে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড পাশাপাশি সজ্জিত থাকে, প্রথমে এই নিউক্লিওটাইড গুলোর প্রতিলিপি তৈরী হয় যেটাকে আমরা বলি mRNA তথা মেসেঞ্জার আরএনএ। নামেই বোঝা যায় এই আরএনএ বার্তাবাহক, ডিএনএতে থাকা জেনেটিক ইনফরমেশন বহন করে এরা। mRNA তৈরীর প্রক্রিয়ার নাম ট্রান্সক্রিপশন। এই mRNA পরবর্তীতে রাইবোজমে পৌছায়, সেখানে সংশ্লেষিত হয় প্রোটিন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সলেশন। আমাদের সকল বৈশিষ্ট্যই ঘুরেফিরে এই প্রোটিন তথা পেপটাইডের উপর নির্ভরশীল। হরমোন, এনজাইম, নিউরোট্রান্সমিটার, স্নায়ুকোষ, মস্তিষ্কসহ সবকিছু এই প্রোটিন। যাহোক, এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। দেহের সকল কোষে একই সংখ্যক ক্রোমোজোম এবং একই জিনসেট থাকা সত্ত্বেও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোষ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন আমাদের পেশি কোষ, নিউরন কোষ, অস্থি কোষ, রক্তকোষ প্রভৃতি প্রভৃতি কোষের কাজ আলাদা আলাদারকম। এই বিভিন্নতার উৎপত্তির পিছনে কাজ করে ‘জিন রেগুলেশন’। জিন রেগুলেশন এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মূলত জিনের তিনটি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।
১। জীবদ্দশার কোন সময়ে কোন জিন প্রকট হবে এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাব বিস্তার করবে।
২। সব কোষে একই জিনসেট থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কোষে প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন জিন প্রকট হবে সেটা।
৩। কোনো কোষে থাকা কোনো একটা নির্দিষ্ট জিন কতটুকু প্রকট হতে পারে সেটা।
এই জিন রেগুলেশনের কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কৌশলও রয়েছে। যেমন: এপিজেনেটিক্স, যেখানে পরিবেশের প্রভাবে কোনো একটা প্রকট জিন প্রচ্ছন্ন অবস্থাতেই থেকে যায় আবার কোনো একটা জিন যার প্রচ্ছন্ন থাকার কথা সে প্রকট হয়ে যায়। ডিএনএ মিথাইলেশন এমন একটি এপিজেনেটিক্স সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। এরকমভাবে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরীর সময়ে বা পরে কিংবা ডিএনএ থেকে প্রোটিন সংশ্লেষিত হওয়ার সময়ে বা পরে এমন কিছু বিক্রিয়া বা ঘটনা ঘটে থাকে যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কোষে থাকা ভিন্ন ভিন্ন জিন প্রকট হয় যার ফলে শরীরের কোনো একটা অঞ্চল নির্দিষ্ট কিছু ফাংশন নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ থাকে। একেকটা অঞ্চলের কোষগুলোকে একেকরকম সেল টাইপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন সকল স্নায়ুকোষ একরকম সেল টাইপ, জনন কোষ আলাদা সেল টাইপ, অস্থিকোষও আলাদা সেল টাইপ।
ভিক্টর অ্যামব্রস এবং গ্যারি রাভকুন এই জিন রেগুলেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেল টাইপ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন জিন রেগুলেশনের সম্পূর্ণ নতুন এক কৌশল যা আগে কেউ জানতো না। আমরা সবাই জানি আমাদের কোষে তিন ধরনের আরএনএ থাকে – mRNA, tRNA, rRNA। প্রতি টাইপের আরএনএর কাজ আলাদা আলাদা। জনাব অ্যামব্রস এবং রাভকুন কোষের মধ্যে এক নতুন ধরনের আরএনএ খুঁজে পেয়েছেন যার নাম microRNA। একটু আগেই উল্লেখ করেছিলাম, ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরীর সময় এমন কিছু ঘটতে পারে যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন সেলটাইপ উৎপন্ন হয়। এই “এমন কিছু” মূলত প্রোটিন বাইন্ডিং। যখন কোনো কোষের ডিএনএ থেকে জেনেটিক তথ্যের প্রতিলিপি হিসেবে আরএনএ অর্থাৎ mRNA সৃষ্টি হয় তখন কিছু বিশেষ প্রোটিন উক্ত ডিএনএর কিছু কিছু অঞ্চলে যুক্ত হয় এবং ডিএনএর ওই অংশগুলোর জিন হতে আরএনএ প্রতিলিপি তৈরী হতে বাঁধা দেয়। ফলে একেক স্থানের ডিএনএ হতে প্রাপ্ত প্রতিলিপি একেকরকম। ১৯৬০ সালে প্রথম এই জিন রেগুলেশনের কৌশল আবিষ্কার এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত বহু বহু প্রোটিন শনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো এই জিন রেগুলেশনের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।
আগে ভাবা হতো, আমাদের, মানুষ কিংবা অন্যান্য বহুকোষী জীবের জিন রেগুলেশন মূলত এই প্রোটিন বাইন্ডিং এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কিন্তু ৯০ এর দশকে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে ঘটে বিধির বাম! আগে একটু ইতিহাস জেনে আসা যাক। অ্যামব্রস এবং রাভকুন দুইজন সহকর্মী ছিলেন রবার্ট হরভিটজ ল্যাবে যেখানে তারা নিজেদের পোষ্টডক্টরাল গবেষণা করছিলেন। সেখানে তারা গবেষণা করছিলেন C elegans নামক এক কৃমির উপরে। এই কৃমি আকারে খুবই ছোটো হলেও যারা বায়োলজি নিয়ে খোঁজখবর রাখেন নিয়মিত তারা এই নামের সাথে সুপরিচিত হবেন। গবেষণার নমুনা হিসেবে এদের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে, কারণ এদের শরীরে বিভিন্ন সেল টাইপের উপস্থিতি। অ্যামব্রস-রাভকুন মূলত গবেষণা করছিলেন এলিগ্যান্সের বিভিন্ন ধরনের টিস্যুর গঠন নিয়ে, তারা এলিগ্যান্সের দেহে এমন জিন খুঁজছিলেন যা সঠিক সময়ে এদের কোষের বিভিন্ন জেনেটিক প্রোগ্রাম চালু করে দেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সেলটাইপের সৃষ্টি করে। অ্যামব্রস আর রাভকুন লিন-৪ (lin-4) ও লিন-১৪ (lin-14) জিন দুটি নিয়ে কাজ করেছিলেন সেইসময়। এই লিন-৪ জিনটি লিন-১৪-এর কাজে বাধা দেয়- এটুকু তারা বুঝতে পারেন। প্রশ্ন হলো এটা কীভাবে ঘটে?
রাভকুন যে বিষয়টি প্রমাণ করে দেখান সেটা হলো লিন-১৪ জিন থেকে ঠিকঠাকমতো ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA তৈরী হয়, কোনোরকম সমস্যা হয়না। সমস্যা শুরু হয় mRNA তৈরী হওয়ার পরে। লিন-৪ থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে যে আরএনএ তৈরী হয় সেখানে একটা কোডন অনুপস্থিত থাকে, ফলে এটা থেকে কখনো প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়না, এই আরএনএ গুলোকে বলা হয় micro RNA। লিন-১৪ থেকে সৃষ্ট mRNA তে একটা বিশেষ অংশ থাকে যেটা লিন-৪ এর micro RNA এর সাথে যুক্ত হয়, যার দরুণ এই mRNA অকার্যকর হয়ে পড়ে। জিন নিয়ন্ত্রণের এই কৌশল ছিলো একদমই নতুন। অ্যামব্রস-রাভকুনের এই অসাধারণ আবিষ্কারের কথা ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হলেও এটা বিজ্ঞানমহলে খুব সাড়া ফেলেনি। লিন-৪ এবং লিন-১৪ এমন দুটি জিন যা এলিগ্যান্স কৃমির দেহেই পাওয়া যায়। ফলে সবাই ভেবে নেয় micro RNA শুধু এলিগ্যান্সের জিন নিয়ন্ত্রণের কৌশল।
২০০০ সালে রাভকুন এবং তার সহকর্মীরা এই গবেষণাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তারা লেট-৭ নামক একটি জিন হতে micro RNA তৈরীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। এই জিন অত্যন্ত বিশেষ, এই জিন বিবর্তনের ধারায় “কনজার্ভড”, গত ৫০ কোটি বছরে এই জিনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। যার দরুন এই জিন মানুষ সহ ছোট-বড় অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীতে পাওয়া যায়। এই জিন হতে micro RNA সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হলো এসকল প্রাণীতে micro RNA দ্বারা জিন নিয়ন্ত্রণের কৌশলও অবশ্যই এক্সিস্ট করবে। এরপর অতিবাহিত হয়েছে প্রায় ২ যুগ। আমরা এখন মানুষের শরীরে উপস্থিত হাজারের উপরে জিনের কথা জানি যেগুলো থেকে micro RNA সৃষ্টি হয় এবং জিন রেগুলেশনে এদের ভূমিকা সর্বজনীন। micro RNA এর মাধ্যমে জিন রেগুলেশন মিলিয়ন বছর ধরে প্রাণীজগতে চলছে। যেকোনো প্রাণীর শরীরের টিস্যুর গঠন, বৃদ্ধি এবং সঠিকভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য এই micro RNA এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই আরএনএ তে বিভিন্ন সমস্যার দরুণ ক্যানসার, জন্মগত বধিরতা, চোখ ও হাড়ের বিভিন্ন রোগের জন্ম হয় মানবশরীরে। এই আরএনএ কে আমরা যতবেশি জানবো আরএনএ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর নিরসনও তত দ্রুত সম্ভব হবে। এটা নিঃসন্দেহে বড় এক সাফল্য বিজ্ঞানের, কৃমি থেকে হওয়া এক অপ্রত্যাশিত সফলতা অ্যামব্রোস-রাভকুন জুটিকে এনে দিয়েছে ২০২৪ এর নোবেল পুরষ্কারও!