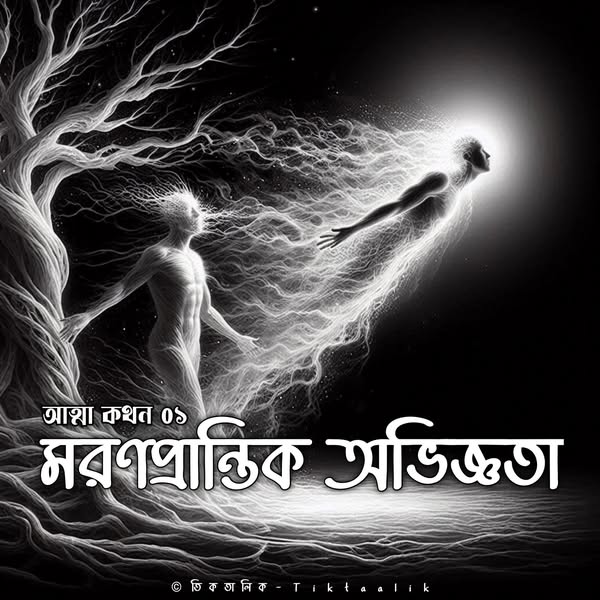সাল ১৯৬৮। চার্লস টার্ট এক অভূতপূর্ব পরীক্ষার চিন্তা করেন। তিনি এক মৃত্যু পথযাত্রী রোগীকে EEG মেশিনের সাথে যুক্ত রেখে ব্রেন ওয়েভ পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণের সময় তিনি রোগীর বিছানার পাশে একটা তাকের সাথে কাগজে একটা সংখ্যা লিখে লেপ্টে রেখে দেন। তিনি মূলত দেখতে চেয়েছিলেন, রোগী সঠিক সংখ্যাটা স্বচক্ষে না দেখে বলতে পারেন কিনা। এই পরীক্ষা তিনি পরপর কয়েকদিন সম্পন্ন করেন। রোগী প্রথম তিন বার সংখ্যাটা বলতে না পারলেও চতুর্থ বারে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক সংখ্যাটাই বলে দেন। অবিশ্বাস্য না? উল্লেখ্য, টার্ট উক্ত রোগীর আসল পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে “মিস জেড” নামে সম্বোধন করেছিলেন।
টার্টের এই পরীক্ষা চালানোর পিছনে মূল কারণ ছিলো যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বহু মানুষের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা (Near Death Experience) এবং অভিজ্ঞতার গল্প। রেমন্ড মুডি ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম এই NDE নামক টার্মটির আবির্ভাব ঘটান। কোনো জটিল সার্জারী, দুর্ঘটনায় অজ্ঞান কিংবা সাময়িক কোমা থেকে বেঁচে ফিরে আসার পর অনেক রোগীই নানারকম গল্প শুনিয়ে থাকেন। কেউ বলেন তিনি অনুভব করেছেন নিজ শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সারা অপারেশন থিয়েটর ঘুরে বেড়ানোর ঘটনা, নিজ চোখে দেখেছেন নিজের অপারেশন হতে। আবার কেউ বলেন তিনি তো ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেয়ে গেছিলেন প্রায় প্রায়। আবার কেউ কেউ নিজের অতি প্রিয়জন, যিনি আর জীবিত নেই তার দেখা পেয়ে যান এই সময়ে। দেহ যখন অসাড় হয়ে থাকে তখন এইসকল অভিজ্ঞতা ঘটে বলে এগুলোকে “আউট অব দ্য বডি এক্সপিরিয়েন্স” ও বলা হয়। রেমন্ড মুডি এসকল ঘটনাকে “মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা” নামকরণের সময় বলেছিলেন, “আধ্যাত্মিক ঘটনা এগুলো, হঠাৎ-ই ঘটে যায় কারোও সাথে। কেউ আমন্ত্রণ জানায় না এসব অভিজ্ঞতাকে। এসব ঘটনা কিছু মানুষের ক্ষেত্রেই শুধু ঘটে যখন তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা।”
এমনটা কেনো ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গিয়ে আগেকারদিনের মানুষজন (বর্তমানেও বহু মানুষ) আত্মার ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, সম্পূর্ণ ঘটনার ব্যাখা আত্মা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, এরকম মুমূর্ষু অবস্থায় আত্মা আমাদের শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আলাদা হওয়ার পর আত্মা যেসব জিনিস দেখে, শুনে, অনুভব করে- সেসব জিনিসই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা হিসেবে আমাদের মননে রয়ে যায়। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষজনের এরকম দাবী কতটা যৌক্তিক তারই খোঁজ করছিলেন চার্লস টার্ট। মিস জেড যখন চতুর্থবারের চেষ্টায় সংখ্যাটা বলতে পারেন তখন সাদা চামড়ার চোখে “আত্মার গল্প সত্য প্রমাণিত হয়েছে” বলে মনে হলেও এখানে রয়ে গেছে ইতং বিতং! আর এই ইতং বিতং ধরা পড়ে EEG মেশিনে। “দি মিম মেশিন” বইয়ের লেখিকা সুসান ব্লাকমোর লিখেছেন, “মিস জেড স্পষ্টত EEG মেশিনের কোনো ইলেকট্রোড না খুলে বিছানা থেকে উঠে সংখ্যাটা দেখেছিলেন। তার ব্রেন ওয়েভের গ্রাফেই সেটা বোঝা যায়।” উল্লেখ্য, টার্ট কেনো উক্ত রোগীর কক্ষে ক্যামেরা রাখেননি রোগীর উপর নজর রাখতে তা নিয়েও বহু সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন তিনি।
ব্রুস গ্রেসন। একজন আমেরিকান মনোচিকিৎসক এবং মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক। তিনি “জাইগোন” এর জুন, ২০০৬ সংস্করণে একটি আর্টিকেলে রেমণ্ড মুডির কাজের কিছু অংশ তুলে ধরেন। মুডি দেখেছেন, মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতায় মোটাদাগে ১৫ টা জিনিস চিহ্নিত করা যায় যা বিভিন্ন রোগী বিভিন্ন সময়ে অনুভব করেছেন।
- পরিষ্কার শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলতে না পারা
- অদৃশ্য কাউকে মৃত্যুর কথা বলতে শোনা
- নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শোনা
- অদ্ভুত মানসিক শান্তি অনুভব করা
- ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের দেখা পাওয়া
- একটা সরু, অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে চলছে এমন অনুভব করা
- সুড়ঙ্গ দিয়ে চলা শেষে হঠাৎ চোখ ঝলসানো প্রচুর আলোর দেখা পাওয়া
- নিজের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি বারবার ভেসে ওঠা যেনো রোগী অতীতে ফিরে গেছেন
- নানাধরনের অলৌকিক সত্ত্বা যেমন: মৃতের আত্মা কিংবা পিশাচের দেখা পাওয়া
- একটা অদ্ভুত নির্দিষ্ট সীমারেখা দেখতে পাওয়া যেনো দুই আলাদা জগতের সীমানা
- নিজের শরীরে পুনঃপ্রবেশ ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি…………
মুডি হিসেব করে দেখেন একই সাথে একজন রোগীর অভিজ্ঞতায় ১৫ টির সবগুলো উপাদান উপস্থিত থাকেনা কখনো। সর্বোচ্চ ১২ টি উপাদানের উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন তিনি একজন রোগীর বর্ণনায়। এ থেকে বলা যায়, সবার অভিজ্ঞতা কখনো হুবহু একইরকম হয় না। এই ১৫ টি অভিজ্ঞতাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। চেতনা সম্পর্কিত, আবেগ সম্পর্কিত, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সম্পর্কিত এবং অতিন্দ্রীয় অনুভূতি সম্পর্কিত। ১৫ টি উপাদানের সবগুলো সবার মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় না থাকলেও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে কিছু না কিছু থাকেই সবার বর্ণনায়। উল্লেখ্য, ১৯৮২-১৯৮৪ এর পরিসংখ্যান অনুসারে আমেরিকার মুমূর্ষু রোগীদের প্রতি তিনজনে একজন এইরকম অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয় বলে মনোচিকিৎসকরা উঠে পড়ে লেগে যান এইসব অভিজ্ঞতার রহস্যোদ্ধারে।
ব্রুস গ্রেসন ঠিক করলেন এ অভিজ্ঞতার গল্পগুলো আসলেই কতটা বাস্তবতা আর কতটা মুমুর্ষু অবস্থায় মনোবৈকল্যতা, সেটা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তার ল্যাপটপটি সাথে নিয়ে এলেন আর তাতে প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রঙ্গীন ছবি (যেমন, উড়োজাহাজ, নৌকা, প্রজাপতি, ফুল ইত্যাদি) বিক্ষিপ্তভাবে ফুটিয়ে তুললেন।তারপর তিনি ল্যাপটপটিকে স্থাপন করলেন হাসপাতালের হার্টের অস্ত্রপ্রচার কক্ষের ছাদের কাছাকাছি কোথাও – এমন একটা জায়গায় যেখানে অস্ত্রপ্রচারের সময় রোগির দৃষ্টি পৌছায় না, একদম টার্টের পরীক্ষার মতোই। দেহবিযুক্ত হয়ে আত্মা যদি আসলেই সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেড়ায় তবে রোগীর দেখতে পাওয়ার কথা এসব ছবি। গ্রেসন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার দাবীদার এরুপ পঞ্চাশ জন মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি চালনা করলেন, কিন্তু একজন রোগীও সঠিকভাবে ল্যাপটপের ছবিগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। ঠিক একই ধরণের পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জ্যান হোল্ডেন। তিনিও গ্রেসনের মতই নেগেটিভ ফলাফল পেলেন।
সুসান ব্ল্যাকমোরের কথা মনে আছে? একটু আগে টার্টের গবেষণার গল্প যখন বলছিলাম তখন এনার নাম উঠে এসেছিলো একবার। সুসান ব্ল্যাকমোর মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিশেশজ্ঞ একজন মনোবিজ্ঞানী, ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। তিনি ‘ডাইং টু লিভ’, ‘ইন সার্চ অব দ্য লাইট’ এবং ‘মিম মেশিন’ সহ বহু বইয়ের প্রণেতা। তিনি তার ‘ডাইং টু লিভ : নিয়ার ডেথ এক্সপেরিএন্স’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিন বন্ধুর সাথে মিলে মারিজুয়ানা সেবন করে কীভাবে একদিন তার ‘আউট অব বডি’ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কীভাবে তিনি টানলের মধ্য দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছিলেন, অক্সফোর্ডের বিল্ডিং এর বাইরে ভাসতে ভাসতে আটলান্টিক মহাসগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে পৌছিয়েছিলেন, তারপর আবার নিজের দেহে ফিরে গিয়েছিলেন। তার এ অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে The Archives of Scientists’ Transcendent Experiences (TASTE) ওয়েবসাইটেও। কিন্তু সুসান ব্ল্যাকমোর যা করেননি তা হল অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গের মতো ‘আধ্যাত্মিকতার অপার মহিমায়’ আপ্লুত হয়ে যাওয়া, কিংবা এঘটনার পেছনে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্রষ্টা, আত্মা কিংবা পরজগতের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া । বরং তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে এসবের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং উপসংহারে পৌছিয়েছেন যে, মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো কোনো পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং এগুলোকে ভালমত ব্যাখ্যা করা যায় স্নায়ু-রসায়ন, শারীরতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে।
উপরে উল্লিখিত “জাইগোন” এর আর্টিকেলে গ্রেসন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখা নিয়ে আলাপ করেন। তিনি প্রথমে একটি শারীরতত্বীয় মডেলের কথা লিখেছেন যেখানে বলা হয়েছে, হাইপোক্সিয়া এবং অ্যানোক্সিয়া এরকম অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে। হাইপোক্সিয়া সেই অবস্থাকে নির্দেশ করে যখন শরীরের বিভিন্ন অংশের টিস্যুতে অক্সিজেন সরবাহ কমে যায়। আর অ্যানোক্সিয়া এমন অবস্থা যখন পুরোপুরিই অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে বলা চলে। এই হাইপোক্সিয়া এবং অ্যানোক্সিয়ায় অনেক ভয়াবহ-ভীতিকর ভ্রমের জন্ম হয় মস্তিষ্কে। সমস্যাটা এখানে। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার গল্পে যেসব ভ্রমের কথা শোনা যায় তা একরকম শান্তিপূর্ণ বলা চলে। কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে যে ভ্রমের জন্ম হয় তা অত্যন্ত কষ্টকর। তাই এই মডেল অতো গ্রহণযোগ্য নয়।
দ্বিতীয় মডেল হিসেবে গ্রেসন লিখেছেন মেডিকেশনের কথা। এবং এই মডেল কিছুটা সাকসেসফুল। আসলেই কিছু ওষুধের এমন ভ্রম সৃষ্টির সক্ষমতা পাওয়া গেছে যা মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে এসব ওষুধ এবং কোনোরকম মেডিকেশন নেয়নি এমন রোগীও মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লব্ধ করেছেন। যার দরুণ বলা চলে ওষুধ কোনোভাবেই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়।
তৃতীয় মডেল হিসেবে সবচেয়ে উপযোগী সম্ভাবনা ব্যাখা করেছেন গ্রেসন। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা আসলে সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে এন্ডোর্ফিন। পরবর্তীতে দেখা যায়- সেরোটনিন, অ্যাড্রেনালিন, ভ্যাসোপ্রেসিন প্রভৃতিরও ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যক্ষ গবেষণায় দেখা যায়, মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত। এসব অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে- টেম্পোরাল লোব, ফ্রন্টাল লোবের মনোযোগ নিয়ন্ত্রক অঞ্চল, প্যারাইটাল লোবের অরিয়েন্টেশন অঞ্চল, থ্যালামাস, অ্যামাগডালা এবং হিপ্পোক্যাম্পাস। এই প্রত্যক্ষ গবেষণার ফলে আলোচ্য বিষয়ের কিছু বস্তুগত প্রমাণ আমাদের সামনে উঠে আসে। বিষয়টা যে, আত্মা নামক কোনো কল্পিত সত্ত্বার কারচুপি না, শুধুই মস্তিষ্কের খেলা তাও স্পষ্ট হয়।
মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা যে আহামরী বিশেষ কিছু না তা বোঝা যায় মৃগী এবং মাইগ্রেনের রোগীদের কেস স্টাডি করলে। তারাও অসুস্থতার সময় ভ্রমের শিকার হন, বিভিন্ন সু্রঙ্গ দেখতে পান। কেন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোতে কেবলই টানেল বা সুরঙ্গ দেখা যায়? কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষজন বলেন, ওটি ইহজগত আর পরজগতের সংযোগ পথ। মৃত্যুর সময় আত্মা এই সুড়ঙ্গ দিয়েই ইহজগৎ হতে পরজগতে গমণ করে। সুড়ঙ্গের পেছনে আলোর দিগন্ত আসলে পরজগতেরই প্রতীকী রূপ। বাস্তবে এমন কিছুই নয়। উপরে সুশান ব্লাকমোরের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি। এলএসডি, সাইলোকিবিন কিংবা মেসকালিনের মত ড্রাগ-সেবনে এমন সুড়ঙ্গের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুজীববিজ্ঞানী জ্যাক কোয়ান ১৯৮২ সালে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে গানিতিক মডেলের সাহায্যে ব্যাখা করেছেন। তার মডেলের সাহায্যে কোয়ান দেখিয়েছেন, কর্টেক্সে ডোরা দাগ থাকলে তা আমাদের চোখে অনেকটা সর্পিল কুন্ডলী আকারে রূপ নেবে। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লাভের সময় প্রায় একই রকম বিভ্রম ঘটে মস্তিস্কের মধ্যেও। ড্রাগ সেবনের ফলে কিংবা অত্যদিক টেনশনে কিংবা অন্য কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে ভিজুয়াল কর্টেক্সের গতিপ্রকৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এ সময় ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই সুড়ঙ্গ-সদৃশ নকশার দর্শন পেয়ে থাকেন। এটাই সুরঙ্গ-দর্শনের মূল কারণ, কোনো ইহকাল-পরকালের রাস্তা নয়।
কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিশেষজ্ঞ কেভিন নেলসন তার গবেষণায় দেখিয়েছিলেন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার জন্য ঠিক সেই কারণগুলোই দায়ী যেগুলো লুচির ড্রিমিং-এর সাথে সম্পর্কিত। নেলসন দেখিয়েছিলেন ঘুমের সময় যদি মস্তিষ্কের ডর্সোল্যাটারাল প্রি-ফ্রন্টাল অঞ্চলটি জাগ্রত হয়ে যায় তবে তা আমাদের স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই ডর্সোল্যাটারাল অঞ্চলটিই আমাদের মস্তিষ্কের যুক্তির কারখানা, আমরা যখন জেগে থাকি এই অঞ্চলই দিনের সকল চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘুমের সময় এই অঞ্চল জাগ্রত হওয়ার অর্থ তখন আমরা ঘুমন্ত অবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান করছি। নেলসনের হিসেবে এই একই অঞ্চলের প্রভাবে, একই প্রক্রিয়ায় কেউ মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। নেলসনের এই গবেষণাকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছেন রাডুগা। তিনি ১০-২০ জনের চারটি ছোটো ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরী করেন এবং তাদের লুসিড ড্রিমিং এর জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এবার তিনি তাদের লুসিড ড্রিমিং এর সময় সেসব কাজ-কল্পনা করতে বলেন যেগুলো সাধারণত মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে বলে এসেছেন এবং প্রবন্ধে আগেও উল্লেখ করেছি আমরা। রাডুগার ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ১৮ জন এই কাজে সফল হয়েছেন। তারা গভীর ঘুমের মধ্যে লুসিড ড্রিমিং এর সাহায্যে সুরঙ্গ, স্বর্গীয় আলো, পূর্বপুরুষদের আত্মা, ঐশ্বরিক নিদর্শন সবকিছুই উপভোগ করেছেন বলে জানান। অর্থাৎ নেলসনের ধারণা রাডুগা সঠিক প্রমাণ করেন। লুসিড ড্রিমিং এবং মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের একই কার্যকলাপের ফসল এবং লুসিড ড্রিমিং এর সাহায্যে এই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লব্ধ করা যায়।
মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা আগে অনেকেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যবহার করতো। আধুনিক বিজ্ঞানে যেমন আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই, একইভাবে মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার হাতেকলমে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণও রয়েছে আমাদের কাছে। এমন আরও বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধ পড়তে তিকতালিকের সাথে থাকুন। কোন কোন বিষয়ে আমরা এমন গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখতে পারি তা আমাদের সাজেশন দিতে পারেন কমেন্টে। আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য কাম্য।
লেখক: তিকতালিকীয় সদস্যবৃন্দ।
উৎসর্গ: অভিজিৎ রায়, একজন প্রয়াত বিজ্ঞানমনষ্ক লেখক।