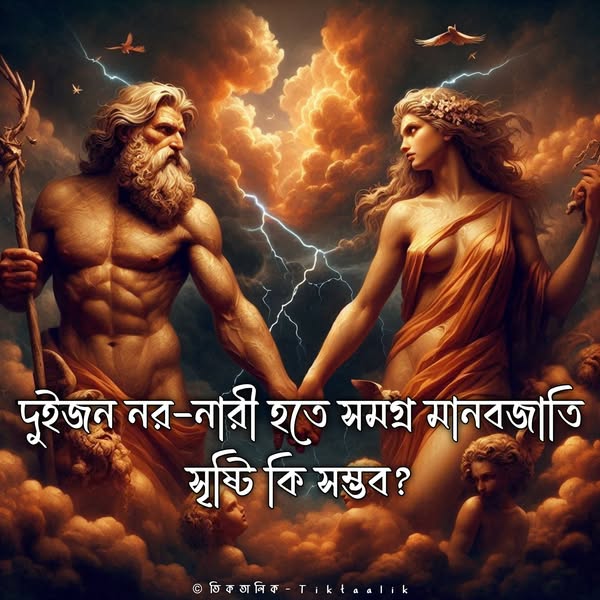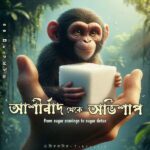সাল ১৭৭৫। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এক দ্বীপ পিনগেলাপে আছড়ে পড়ে এক ভয়াবহ তুফান। এই তুফানে আক্রান্ত হয়ে ঐ দ্বীপের প্রায় পুরো জনবসতিই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছিলো। মাত্র ২০ জনের মতো মানুষ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছিলো সেদিন ঐ দ্বীপে। আজকের দিনে পিনগেলাপে যে জনগোষ্ঠী আমরা দেখতে পাই তাদের সবার পূর্বপুরুষ ঘুরেফিরে ঐ ২০ জনই। ঐতিহাসিকদের মতে, ওই ২০ জনের মধ্যে একজন ছিলেন সেই জনগোষ্ঠীর শাসক, তার ছিলো বর্ণান্ধতার জিন। তুফান শেষে রাজা অনেক বেশি সংখ্যায় বাচ্চা উৎপাদন করেন যাদের মধ্যেও এই জিন প্রবাহিত হয়, তাদেরও অনেকে ছিলেন বর্ণান্ধ, অনেকের মধ্যে আবার প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলো এই জিন। রাজার ছেলেদের কাছেও প্রচুর বাচ্চা উৎপাদনের সুযোগ থাকায় এই জিনের প্রবাহ সূচকীয় হারে বাড়তে থাকে। ফলে আজকের দিনে ঐ পিনগেলাপ দ্বীপের প্রায় ১০% মানুষ এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত। পৃথিবীর হিসেবে যেখানে গড়ে প্রতি ৩০,০০০ এ মাত্র একজনের এই বর্ণান্ধতা দেখা যায় সেখানে যদি উক্ত দ্বীপে যদি ৩০,০০০ সদস্য থাকতো তবে বর্ণান্ধ মানুষের সংখ্যা হতো ৩০০০ জন! অর্থাৎ সাধারণের তুলনায় প্রায় ৩০০০ গুণ বেশি বর্ণান্ধতার প্রকোপ এখানে। এর কারণ একটাই, খুব অল্পসংখ্যক পপুলেশন থেকে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর পুনুরুত্থান।
আরেকটা উদাহরণ হিসেবে আনা যায় স্পেনের হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের পতন। এই সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফিলিপ। এই সম্রাজ্য ফিলিপসহ আরও ১৫ প্রজন্ম টিকে থাকার পরে চার্লস II এর মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে যায়। এই সম্রাজ্য সমাপ্ত হওয়ার কারণ ছিলো নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের প্রচলন। এই সম্রাজ্যের রাজবংশে সর্বদাই চাচাতো-খালাতো ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজি এর মতো দ্বিতীয় মাত্রিক আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো। উল্লেখ্য, পিতা-মাতা, ভাই-বোন হলো প্রথম মাত্রিক আত্মীয় এবং চাচা-কাকা, ফুফু-খালা, মাসি-পিসি, চাচাতো মামাতো খালাতো ভাই বোনেরা হলো দ্বিতীয় মাত্রিক আত্মীয়। আত্মীয় নয় এমন কোনো সঙ্গীর সাথে মিলনে উৎপন্ন সন্তানের তুলনায় দ্বিতীয় মাত্রার আত্মীয়দের সাথে মিলনে উৎপন্ন সন্তানে জেনেটিক রোগের সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে। আবার, দ্বিতীয় মাত্রার আত্মীয়দের সাথে উৎপন্ন সন্তানের তুলনায় প্রথম মাত্রার আত্মীয়দের সাথে মিলনে প্রাপ্ত সন্তানে এই জিনগত সমস্যার সম্ভাবনা আরও বেশি। কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সম্ভাবনা বেশি হবে সেটা যে প্যারামিটার দেখে বোঝা যায় তাকে বলে “ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন”, বারবার দ্বিতীয় মাত্রার আত্মীয়দের সাথে মিলিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকলে প্রতি প্রজন্মে এই ইনব্রিডিং ডিপ্রেশনের সাংখ্যিক মান বাড়তে থাকে। ফিলিপ I এর ক্ষেত্রে এই মান যেখানে ০.০২৫ ছিলো, ১৬ তম জেনারেশন অর্থাৎ চার্লস II এর ক্ষেত্রে সেই মান হয়েছে ০.২৫৪। শুধু চার্লসের বেলায় নয়, হ্যাবসবার্গ সম্রাটদের শেষ কয়েক প্রজন্মের অনেকেরই ইনব্রিডিং ডিপ্রেশনের সাংখ্যিক মান ০.২ এর উপরে, যা দুর্লভ জিনগত রোগে আক্রান্ত হওয়াকে ভবিতব্য করে দেয়। চার্লস দুটি ভিন্ন জেনেটিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন- পিটুইটারি হরমোন ডেফিসিয়েন্সি এবং রেনাল টিউবলার অ্যাসিডোসিস। এছাড়া তিনি সন্তান জন্মদানেও অক্ষম ছিলেন। ফলে ১৭০০ সালে যখন চার্লস মারা যান তখন তার সাথে সাথেই হ্যাবসবার্গ সম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে এবং নতুন যুগের শুরু হয়।
উপরে উল্লিখিত দুই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি, কোনো গোষ্ঠী সংখ্যায় যত ছোটো হবে, তত মিলনের জন্য সঙ্গী হিসেবে অজাচারকে বেছে নিতে হবে, হোক সেটা বাধ্য হয়ে (প্রথম উদাহরণ) কিংবা হোক সেটা খুশিমনে, পছন্দ করে (দ্বিতীয় উদাহরণ)। অজাচার তথা ইনসেস্টের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটালে কয়েক প্রজন্ম পরে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান কিংবা অন্যান্য জেনেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কারণ হোমোজাইগোসিটি। যেসকল প্রাণী যৌন জননের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে তাদের ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমাটিড পিতা থেকে এবং অপরটি আসে মাতা থেকে। ধরি, কোনো বংশের মাতা এবং পিতা উভয়ই লম্বা এবং তাদের শরীরে রয়েছে Tt জিনোটাইপ যার দ্বারা এই উচ্চতা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে T অ্যালিল প্রকট (dominant) এবং t অ্যালিল প্রচ্ছন্ন (recessive), প্রকট অ্যালিলই সর্বদা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ T অ্যালিলকে প্রাণীর উচ্চতা বেশি হওয়ার জন্য এবং t অ্যালিলকে প্রাণীর উচ্চতা কম হওয়ার জন্য দায়ী অ্যালিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মাতা পিতার মিলনের ফলে যে জাইগোট তৈরী হবে সেখানে চার ধরনের জিনোটাইপ হওয়া সম্ভব।
i) মাতার T এর সাথে পিতার T, ফলাফল লম্বা সন্তান।
ii) মাতার T এর সাথে পিতার t, ফলাফল লম্বা সন্তান।
iii) মাতার t এর সাথে পিতার T, ফলাফল লম্বা সন্তান।
iv) মাতার t এর সাথে পিতার t, ফলাফল খাটো সন্তান।
T প্রকট অ্যালিল হওয়ায় TT, Tt এই দুই কম্বিনেশনেই T প্রকট বৈশিষ্ট্য লাভ করবে এবং t প্রচ্ছন্ন রূপে ক্রোমোজোমে থেকে যাবে। অর্থাৎ জিনোটাইপে T থাকলেই ঐ সন্তানদের উচ্চতা বেশি হবে। যাহোক, উপরের চারটা জিনোটাইপের (i) ও (iv) নম্বরে আমরা যে TT কিংবা tt জিনোটাইপ দেখতে পাচ্ছি, এদেরকে বলা হয় হোমোজাইগাস অ্যালিল তথা হোমোজাইগোসিটি। কারণ এই দুই কম্বিনেশনে থাকা উভয় অ্যালিল হবহু একই। দুইটাই হয় প্রকট নাহলে দুইটাই প্রচ্ছন্ন। একইরকম অ্যালিল হওয়ায় হোমোজাইগাস এদের নাম। আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলতে চাইলে TT কে বলা যায় হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট। এই জিনোটাইপধারী প্রাণীর উচ্চতা বেশি হবে। অপরদিকে, tt হলো হোমোজাইগাস রেসিসিভ। এই জিনোটাইপধারী প্রাণী হবে খাটো।
অন্যদিকে, Tt একমাত্র কম্বিনেশন এখানে হেটেরোজাইগাস অ্যালিলের। ফলে, কোনো প্রাণীতে হেটেরোজাইগাস অ্যালিল থাকা মানেই তার উচ্চতা বেশি, প্রকট অ্যালিল T এর উপস্থিতির জন্য। ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন তথা অজাচারজনিত জেনেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেই এই হোমোজাইগোসিটির জন্য যেখানে হেটেরোজাইগোসিটি আমাদের প্রকৃতিতে টিকে থাকার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কীভাবে? সরাসরি বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক তাহলে।
মানুষের ক্রোমোজোমে HbA, HbS দুইটি অ্যালিল, যাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি “শিকল সেল অ্যানেমিয়া” রোগের জন্য দায়ী। HbA অ্যালিল HbS এর উপর ডমিন্যান্ট অ্যালিল হিসেবে কাজ করে। এই অ্যালিলদ্বয় হতে প্রাপ্ত জেনেটিক কম্বিনেশন তিনটি হলো HbA HbS, HbA HbA, HbS HbS।
ছোটোবেলার বিজ্ঞান বই থেকে আমরা জানি, আমাদের রক্তে অক্সিজেন পরিবহন করে হিমোগ্লোবিন। মজার বিষয় হলো, HbA সাধারণ সুস্থ বিটা গ্লোবিন প্রোটিন কোড করে। ফলে রক্তে অক্সিজেনের ভালো পরিবহন সুনিশ্চিত হয়। অপরদিকে, HbS অ্যাবনরমাল আকৃতির বিটা গ্লোবিন কোড করে- যা রক্তে অক্সিজেনের সুপরিবহনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আবার এই HbS অ্যালিলের উপস্থিতি ম্যালেরিয়া পরজীবীর জন্য হুমকি। এই অ্যালিল কারোও ক্রোমোজোমে থাকলে তা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সৈনিক হিসেবে আচরণ করে। তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো এমন:
i) যদি জিনোটাইপ হয় HbA HbA –
“শিকল সেল অ্যানেমিয়া”-র প্রতিবন্ধক। কোড করা বিটা গ্লোবিন অক্সিজেনের সুপরিবাহক। কিন্তু, ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।
ii) যদি জিনোটাইপ হয় HbS HbS –
“শিকল সেল অ্যানেমিয়া”-র জন্য দায়ী। কোড করা বিটা গ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহনে খুবই দুর্বল। কিন্তু এরা ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করে।
iii) যদি জিনোটাইপ হয় HbA HbS –
“শিকল সেল অ্যানেমিয়া”-র প্রতিবন্ধক। আবার ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে উভয় সমস্যা থেকেই জিনোটাইপধারীকে রক্ষা করে থাকে।
শেষ হিসাব-নিকাশ কী দাঁড়ালো তবে? কে বেশি উপযুক্ত প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য? এক কথায় উত্তর, হেটেরোজাইগাস অ্যালিল সমৃদ্ধ সদস্য। HbA HbS জিনোটাইপ হলে একই সাথে শিকল সেল অ্যানেমিয়া এবং ম্যালেরিয়া পরজীবী উভয়ের হাত রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যেটা HbA HbA কিংবা HbS HbS হোমোজাইগাস সমৃদ্ধ কেউ পাচ্ছেনা। নিকটাত্মীয়দের সাথে আমাদের জেনেটিক মিল সবচেয়ে বেশি থাকে, ফলে একই জিনোটাইপধারীর সাথে মিলিত হয়ে যে সন্তান গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে হোমোজাইগোসিটি বাড়বে। কয়েক প্রজন্ম পর এই হোমোজাইগোসিটি বাড়তে বাড়তে চার্লস II এর মতো অবস্থা হবে কিংবা পিনগেলাপ দ্বীপের মতো পুরো গোষ্ঠী একই জেনেটিক রোগ বয়ে বেড়াবে। ফলে, টিকে থাকার সম্ভাবনাও কমবে যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন।
কোনো গোষ্ঠীতে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন দূর করার উপায় খুুঁজতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান জীনতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ আইয়ান ফ্রাঙ্কলিন এবং আমেরিকান জীববিজ্ঞানী মাইকেল সল প্রথম ৫০/৫০০ রুলের প্রবর্তন ঘটান। তারা বলেন, কোনো গোষ্ঠীতে যদি কমপক্ষে ৫০ জন সদস্য থাকে তবে ওই গোষ্ঠীতে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন কমে আসে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অধিকতার টিকে থাকার যোগ্য হয়, অর্থাৎ গোষ্ঠীতে হোমোজাইগোসিটির পরিমাণ কমাতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন আদি পিতা বা আদি মাতা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে হোমোজাইগোসিটি যেমন হ্রাস পাবে তেমন হেটেরোজাইগোসিটি বজায় থাকবে এবং সন্তানদের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফ্রাঙ্কলিন-সলের হিসাব অনুসারে ৫০ জন সদস্য নিয়ে কোনো গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হলে সে গোষ্ঠী ভবিষ্যতে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মহামারী রোগে খুব সহজেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কারণ, এরূপ একটি গোষ্ঠীতে যে পরিমাণ জেনেটিক বৈচিত্র্যতা পাওয়া যায় তা আসলে বোটলনেক ইফেক্ট সার্ভাইভ করার মতো নয়। একদম শুরুতে পিনগেলাপ দ্বীপপুঞ্জে ভয়ঙ্কর তুফানের কারণে জনসংখ্যা হঠাৎ হ্রাস পাওয়ার যে গল্পটা বলেছিলাম সেটাই বোটলনেক ইফেক্ট এর উদাহরণ। কোন জনগোষ্ঠীতে যত বেশি জেনেটিক বৈচিত্রতা থাকে তত বেশি তারা কোন মহামারি রোগে টিকে থাকার যোগ্যতা প্রদর্শন করে। একই ধরনের জেনোটাইপ যদি সবার ভিতরে থাকতো, তবে যেকোনো একটি সংক্রামক রোগে পুরো জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি সদস্য আক্রান্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যেতো। ৫০/৫০০ রুল অনুসারে, যদি ইনব্রিডিং ডিপ্রেশনের পাশাপাশি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী রোগ তথা যেকোনো বটলনেক ইফেক্টে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে হয় তবে জনগোষ্ঠীতে কমপক্ষে ৫০০ জন সদস্য থাকতেই হবে। কোন জনগোষ্ঠীর আদি পিতা বা আদিমাতা সংখ্যা ৫০০ জন বা তার অধিক হলে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন থেকে রক্ষার পাশাপাশি লং টার্মে এদের যে কোন প্রকার পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এর খুব সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ আমাদের চোখে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাউদান এলিফ্যান্ট সিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ টি, এই বছরের গবেষণা অনুসারে এই সংখ্যা বের হয়েছে প্রায় দুই লাখ। কিন্তু মাত্র ২৫ জন সদস্য থেকে এত বড় গোষ্ঠীর পুনরুত্থানের ফল হিসেবে দেখা যায় প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যের হুবাহু প্রতিরূপ, এদের মধ্যে না আছে কোনো জিনগত বৈচিত্র্য আর না আছে কোন বৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র্য। ফলে যদি কখনো কোনো মহামারী রোগের প্রকোপ ঘটে তবে নিমেষেই এই এলিফ্যান্ট সিল গোষ্ঠী বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাবে।
এই ৫০/৫০০ রুল আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা দেয় একজন আদি পিতা এবং একজন আদিমাতা হতে একটা পুরো জনগোষ্ঠী কিংবা প্রজাতির উৎপত্তি সম্ভব নয়। তবে পপুলেশন ইকোলজির উন্নতির সাথে সাথে এই হিসাব-নিকাশ আরো জটিল হয়েছে। এই ৫০/৫০০ রুল সবার জন্য, সব প্রজাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। পপুলেশন ভায়াবিলিটি অ্যানালাইসিসের সাহায্যে প্রত্যেক প্রজাতির আলাদা আলাদা MVP নির্ণয় করা সম্ভব। MVP এর পূর্ণরূপ Minimum Viable Population, যা বলতে সেই ন্যূনতম সদস্য সংখ্যাকে বুঝায় যেটা একটা সুস্থ সবল গোষ্ঠী তথা প্রজাতির বিস্তারের জন্য প্রয়োজন। এই সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য গোষ্ঠী বা প্রজাতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনা হয়। যেমন: সদস্যদের গড় আয়ু, কোন সদস্য বছরে কয়বার সন্তান উৎপাদন করে, কত বছর বয়স থেকে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়, একজন তার জীবদ্দশায় কতটি সন্তান উৎপাদন করে, প্রতিটি সদস্য গড়ে কয়জনের সাথে সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যৌন জননে লিপ্ত হয়, কি কি রোগের প্রাদুর্ভাব সবার মধ্যেই দেখা যায় এবং সেসব রোগে প্রতিবছর কি পরিমান মানুষ মারা যায়, সঙ্গী হিসেবে গোষ্ঠীর সদস্যরা নিকট আত্মীয়দের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে কিনা প্রভৃতি। যে সকল গোষ্ঠীর সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে সাধারণত সন্তান উৎপাদন করে না (মানুষ সহ অন্যান্য প্রাইমেট) কিংবা যে সকল গোষ্ঠীর সদস্যরা অতিরিক্ত অজাচারে লিপ্ত হয় (চিতা, হাতি, কিছু মানবগোষ্ঠী) সে সকল গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই MVP অনেক বেশি হয়। অপরদিকে, যে সকল প্রাণী বছরে কয়েকবার সন্তান উৎপাদন করে, অনেক বেশি পরিমাণে সংখ্যা সন্তান উৎপাদন করে কিংবা অজাচারের ঘটনা তেমন একটা দেখা যায় না তাদের ক্ষেত্রে এই MVP কম হয়।
এবার মানুষের ক্ষেত্রে এই MVP নিয়ে একটু চিন্তা করা যাক। পরিস্থিতি অনুসারে এই সংখ্যা অবশ্যই পরিবর্তনীয়। যদি চিন্তা করি আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী এক্সোপ্লানেটে গিয়ে যদি কয়েক প্রজন্ম মানুষ বসবাস করতে চায় তবে ন্যূনতম কতজন মানুষ সেখানে গিয়ে বসতি গড়তে হবে, তবে সেই সংখ্যাটা আসে ৯৮ জন। অর্থাৎ ৯৮ জন মানুষ সেখানে গিয়ে বসবাস করলে, জীবনযাপন করলে, অবাধ যৌন জননের মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করলে বেশ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত যেকোনো পরিস্থিতে মানুষ সেখানে বিলুপ্ত না হয়ে টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। পলিনেশিয়া কিংবা আমেরিকায় যে জনগোষ্ঠী এখন রয়েছে তেমন একটা জনগোষ্ঠী পুনরায় তৈরী করতে হলে প্রায় ৭০ জন আদিপুরুষ প্রয়োজন হবে। যদি প্রকৃতি অনুকূলে থাকে, কোন বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে তবে ১০০-৫০০ জন সদস্যের একটি গোষ্ঠী থেকে টিকে থাকতে সক্ষম এরুপ সুস্থ সবল মানব প্রজাতির বিস্তার পুনরায় সম্ভব। এভাবে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করে বিভিন্ন ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে। তবে, কোনভাবেই একজন আদি পিতা এবং একজন আদি মাতা অর্থাৎ মাত্র দুজন পূর্বপুরুষ হতে হাজার বছর ধরে টিকে থাকার মতো সুস্থ সবল গোষ্ঠী তৈরি হওয়াসম্ভব নয়, সেখানে মানুষের মতো এরকম বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ প্রজাতি অনেক অনেক দূরের বিষয় বলা চলে।
এবার একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। ধরি, দুইজন নারী-পুরুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উত্থান ঘটেছে এবং প্রথম দুজন নারী-পুরুষ যদি একদম আদর্শ অর্থাৎ জেনেটিক্যালি তাদের জিনোমে কোনো রোগ শোকের জন্য দায়ী অ্যালিল নেই। এমন চিন্তা করলে বর্তমান মানবজাতির মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ, টিকে যাওয়া একটা গোষ্ঠী বা প্রজাতি পাওয়া অসম্ভব নাকি সম্ভব? এই চিন্তার সবচেয়ে বড় সমস্যাই হলো “আদর্শ” নারী বা পুরুষ নিয়ে। কোনো প্রাণীরই আদর্শ জিনোটাইপ বলে কিছু হয়না। একটু উপরের ম্যালেরিয়া বনাম শিকল সেল অ্যানিমিয়ার উদাহরণটা ভাবুন। ধরুন, আমাদের আদিপিতা-আদিমাতার জিনোম আদর্শ অর্থাৎ উক্ত দুইটা রোগই প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তাদের মধ্যে থাকবে হেটেরোজাইগাস অ্যালিল HbS HbA, কিন্তু তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে সর্বদা HbS HbA পাবো না। মিলনের ফলে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে চার রকম (পিতার HbS মাতার HbA, মাতার HbS পিতার HbA, দুজনেরই HbA, দুজনরই HbA) জিনোটাইপ পাবো। ফলে দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে যদি ভাই-বোনের বিবাহের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হয়, তবু একই ফলাফলই চলে আসবে আবার, সেই ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন এবং হোমোজাইগোসিটির উত্তরতর বৃদ্ধি দেখা যাবে। অর্থাৎ “আদর্শ” জিনোম বলে এমন কিছুই সম্ভব না যেটার জন্য আলোচিত সমস্যাগুলো কোনো গোষ্ঠীতে দেখা যাবেনা।
আলোচনার শেষপ্রান্তে আমরা। পৃথিবীর অধিকাংশ সম্প্রদায়, ধর্মমত কিংবা বিশ্বাসে একজন নারী এবং একজন পুরুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত বেশিরভাগ মত-বিশ্বাসেও এটি দেখা যায়। ফলে জীবনের একটা বড় সময় এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে পুরো জীবনই কেটে যায় এই বিশ্বাসে। আমরা আজকে আলাপ করলাম কেনো বাস্তবে আসলে এটি হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব উদাহরণ রয়েছে আমাদের হাতে। যদি এমন হতো এবং কোনোভাবে এত বছর যদি আমরা টিকেও যেতাম, তাহলে দেখা যেতো পৃথিবীতে যে ৮ বিলিয়ন মানুষ রয়েছে তারা সবাই একে অপরের হুবহু প্রতিরূপ যেমনটা আমরা নর্দার্ন এলিফ্যান্ট সিলের ক্ষেত্রে দেখেছি উপরের আলোচনায়। অনেকে আজকাল আদিপিতা-আদিমাতার ধারণাকে প্রমাণিত করতে মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভ নিয়ে টানাটানি করেন। পরবর্তী পর্বে আমরা এই মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভ নিয়ে বিস্তার আলাপ করবো। ততদিন যুক্ত থাকুন তিকতালিকের সাথে, বিজ্ঞানের সাথে।
প্রথম পর্ব পড়ার পরেও জানার আগ্রহ মিটেনি? চলুন, জেনে নিই আরও তথ্য। ক্লিক করুন এখানে।
Reference:
→ Wikipedia, Minimal Via Population
→ National Geographic, On Island of the Colorblind, Paradise has a Different Hue
→ Medium, Can Two People Actually Repopulate Earth?
→ BBC, Could just two people repopulate Earth?
→ PLOS ONE, The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty
→ Science Alert, Could Two People Repopulate Earth? Science Weighs in
→ Researchgate, Minimum Viable Human Population with Intelligent Interventions