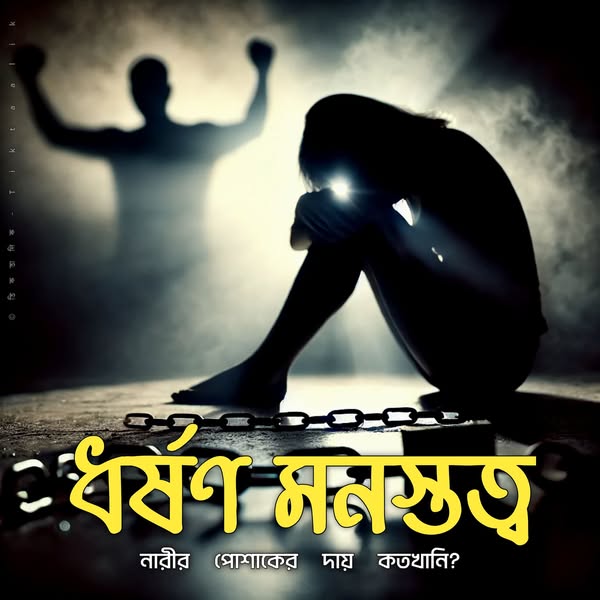ধর্ষণের জন্য কি পোশাক দায়ী? বহুবছর ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল প্রচলিত এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো আজ। এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগে অন্য আরেকটা প্রশ্নের উত্তর ভাবা আবশ্যক। একটা ধর্ষণ কিংবা যৌন নির্যাতন কেনো হয়? এই প্রশ্নের উত্তরও খুব সরল নয়, এর উত্তর কেমন হবে সেটা নির্ভর করে আমরা এই প্রশ্নের মাধ্যমে ঠিক কী জানতে চাচ্ছি সেটার উপর। আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি হয় প্রকৃতিতে কিভাবে ধর্ষণের উৎপত্তি হয়েছে সেটা জানা, তবে সেটার উত্তর একমাত্রিক। শুধুমাত্র নিজের জিনের প্রতিরূপ তথা সন্তান প্রকৃতিতে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ধর্ষণের অভিযোজন। বহু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী (বেডবাগ, মাকড়সা) যাদের মধ্যে যৌন তাড়না নেই, তারাও ধর্ষণের মতো কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। একইভাবে হাঁস, বিভিন্ন ব্যাঙ এবং মাছের প্রজাতি, সামুদ্রিক সিল, সি লায়ন প্রভৃতি নিন্মশ্রেণীর প্রজাতির পুরুষেরা ধর্ষণের মতো আচরণ ধারণ করে থাকে। এদের আচরণে অনুভূতি আবেগ এসবের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য, এরা যা কিছু করে একরকম চিন্তাভাবনা আবেগহীন কোড করা মেশিনের মতো বললেও ভুল হবেনা।
অন্যদিকে আপনার আকাঙ্ক্ষা যদি হয় মানবসমাজে একটা ধর্ষণ কেনো ঘটে সেটা বোঝার তবে সেটার উত্তর বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক উত্তর বোঝার আগে আমাদের একটু মানবসমাজ বিশেষ করে সমাজের উৎপত্তিটা বোঝা দরকার। আমরা ছোটো থেকেই পড়ে আসছি সমাজের একক পরিবার- পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হতে সমাজ। এই পরিবার এবং গোষ্ঠীর উৎপত্তির পিছনে মুখ্য ভূমিকা রাখে আমাদের সহমর্মিতা। জীববিজ্ঞানের ভাষায় আমাদের জীবন একটা নীতি খুবই কট্টরভাবে অনুসরণ করে- Fit enough to survive upto breeding। এর অর্থ- কোনো প্রজাতি যদি টিকে থাকতে চায় প্রকৃতিতে, সেই প্রজাতির সদস্যদের যথেষ্ট উপযুক্ত হতে তো হবেই, সাথে সাথে প্রজননও ঘটাতে হবে। অন্য প্রজাতি কিংবা নিজ প্রজাতির অন্য সদস্যদের তুলনায় উপযুক্ততায় এগিয়ে থাকতে হবে। জৈবিক প্রয়োজন মিটানোতে (যেমন পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ), কিংবা ঝড়-বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় টিকে থাকায় যে যত বেশি দক্ষ হতে পারবে তার টিকে থাকার সুযোগ তত বেশি বাড়বে। এখন একই প্রজাতির সব প্রাণী যখন একই ধরনের খাদ্যের পিছনে ছুটবে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। এই প্রতিযোগিতা খাদ্যের পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়, প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার মতো জৈবিক চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়; আর যখন খাদ্য, সম্পদ, যৌনসঙ্গীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ তখন তা এই অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই প্রতিযোগিতা প্রকৃতির এক নিষ্ঠুরতাই বলা চলে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতম প্রতিযোগিতায় টিকতে গিয়েই সহিংসতার হাত ধরে উৎপন্ন হয়েছে সহমর্মিতার, সহযোগীতার। আমরা আমাদের তুলনায় অনেক নিম্ন প্রজাতির প্রাণীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও এই সহযোগীতার বিষয়টা দেখতে পাই। যেমন: বাঁদুড়েরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে খায়। বানর বা গরিলাদের মধ্যে সহমর্মিতার বিষয়গুলো আরও পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়। জীববিজ্ঞানে হ্যামিলটনের সূত্র নামে একটা সূত্র আছে যেটা প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে উৎপন্ন উক্ত সহমর্মিতা বা পরার্থিতার ঘটনাটা সুন্দরভাবে ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। হ্যামিল্টনের সূত্রের গাণিতিক রূপ এমনঃ
b > c/r
বা, br – c > 0
এখানে, b হলো সাহাযপ্রার্থীর প্রাপ্ত সহায়তা (benefit received by recipient)
r হলো সাহায্যপ্রার্থী এবং সাহায্যকারীর মধ্যে সম্পর্ক (coefficient of relationship)
c হলো সাহায্য করার দরুণ সাহায্যকারীর হারানো সম্পদ (cost of altruism)
একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরুন, একটা সিংহীর শারীরিকভাবে পুষ্ট শাবক আছে। আরেক সিংহীর শাবক খাদ্যাভাবে ভুগছে, প্রায় মৃত অবস্থা। এমতাবস্থায় প্রথম সিংহী যদি মুমূর্ষু বাচ্চাটিকে খাইয়ে দেয় নিজের বাচ্চার খাবার, তবে-
১) মুমূর্ষু বাচ্চাটির জীবন বেঁচে যাবে। এটা হলো ঐ বাচ্চাটির পাওয়া বেনিফিট তথা benifit received by recipient (b)। যেহেতু একজনের পুরো জীবন বেঁচে যচ্ছে তাই এক্ষেত্রে b=1।
২) সিংহী তার পুষ্ট, সবল বাচ্চার খাবার মুমূর্ষু বাচ্চাটিকে খাইয়েছে। ফলে পুষ্ট বাচ্চাটির ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি হবে। এটাকে বলে পরার্থিতা বা সহযোগীতার জন্য মূল্য চুকানো তথা cost of altruism (c)। নিশ্চিতভাবে এক-দুবেলা না খেলে বাচ্চাটা মরে যাবেনা বা বড় কোনো ক্ষতি হবেনা। তাইচ, ধরি c= 0.15।
৩) যেহেতু উভয় একই প্রজাতির তাই তাদের জেনেটিক্যাল মিল আছে স্বাভাবিকভাবেই। ধরি, এই জিনগত সম্পর্ক গড়ে (relatedness, r) r= 0.65।
এখন হ্যামিল্টনের সূত্রে আমরা এই মানগুলো বসাই।
0.65×1-0.15>0 বা, 0.5>0 যা সত্য। এভাবে যেসব ক্ষেত্রে b,c এবং r এর বিভিন্ন মানের জন্য হ্যামিল্টনের অসমতা সত্য হবে সেসব ক্ষেত্রে আমরা পরার্থিতা খুঁজে পাবো।
পরার্থিতা বা সহযোগীতার গাণিতিক যুক্তি তো দেখলাম, এবার একটু বিষয়টা অনুধাবন করা যাক। ন্যাচারাল সিলেকশনে উপযুক্ত থাকার বা সার্ভাইভ করার উদ্দেশ্যটা কী আসলে? প্রজনন ঘটানো। অর্থাৎ নিজের জিন পরবর্তী বংশধরে প্রবাহ করা যেন প্রজাতির টিকে থাকার সুযোগ বাড়ে। এখন উপরের উদাহরণটাই ভাবেন। নিজের সন্তানের পাশাপাশি আরেকজনের সন্তানকে বাঁচানোর ফলে জিনের প্রবাহ আর প্রজাতির টিকে থাকার সুযোগ অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে। এটাইতো লক্ষ্য। সামগ্রিক ফিটনেস বাড়ানো। এভাবেই পরার্থিতার মাধ্যমে ইনক্লুসিভ ফিটনেস লাভ করা যায়। আর তাই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে প্রতিযেগীতা, দ্বন্দ্ব থাকলেও সার্বিক কল্যাণে সহমর্মিতার উদ্ভব ঘটে।
হ্যামিল্টনের সূত্র থেকে আরও কিছু অনুসিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে।
১) b=0 হওয়ার সুযোগ নেই। কারও উপকার হচ্ছে সহমর্মিতায়। সুতরাং কিছুনা কিছু মান তো থাকবেই b এর।
২) r=0 হবেনা। কারণ একই প্রজাতির প্রাণীদের মাঝে জেনেটিক রিলেশন তো আছেই, সব প্রজাতির জীবের মধ্যে জিনোম সিকোয়েন্সে কিছু সাদৃশ্য পাবো আমরা।
৩) b এবং r এর মান যেহেতু 0 হবেনা সহমর্মিতায় তাই c এর মান 0 হলে সর্বোচ্চ সহমর্মিতা বা পরার্থিতা দেখা যাবে।
তবে হ্যামিল্টনের সূত্রের হিসাব-নিকাশ অনেক জটিল। আমরা শুধু একটা উদাহরণ দেখেছি মাত্র, তাও মাত্র একজন গ্রহীতা আর একজন দাতা দিয়ে। গোষ্ঠী পর্যায়ে অবশ্যই এই হিসাব-নিকাশ করতে কিংবা b, c এর স্টান্ডার্ড মান বের করতে অনেক খাটুনি খাটতে হয় বিজ্ঞানীদের। আর পরার্থিতার সবদিক সঠিকভাবে ব্যাখ্যার জন্য হ্যামিল্টনের সুত্রের পাশাপাশি গেম থিওরীর মতো আরও বহু জীববৈজ্ঞানিক মতবাদের সহায়তার দরকার। যাহোক, এই সহমর্মিতা পরার্থিতার মাধ্যমে টিকে থাকায় যে সুবিধাটা পাওয়া যায় সেই সুবিধালাভের আশাতেই উৎপত্তি হয় পরিবারের, আবির্ভাব ঘটে গোষ্ঠীর। অনেক প্রাণীই গোষ্ঠী আকারে বসবাস করে, একসাথে থাকতে গেলে মূলত একটা নীতিই অনুসরণ করতে হয়- “দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ।” দশজনের একটা দল, সবাই একসাথে কাজ করে। খাদ্য সংগ্রহ, শিকার, বাসস্থান বানানো, জংলী জানোয়ার থেকে নিজেদের রক্ষা করা, দুর্যোগে টিকে থাকা সব ক্ষেত্রেই সুবিধা পাওয়া যায়। ধরুন, আপনি একা এই কাজগুলো সব করছেন। অপরদিকে দশজনে মিলে করছেন। নিজে চিন্তা করলেই সুবিধাগুলো বুঝে যাবেন। আর এরকম গোষ্ঠী আকারে বসবাস করার প্রচলন মানুষের মাঝেই শুধু দেখা যায় এমন না এটা আমরা সবাই কমবেশি জানি।
আবার এই গোষ্ঠীর মধ্যে আছে প্রতারক। সেটা থাকাও স্বাভাবিক। সহমর্মিতার উদ্ভব ঘটলেও জিনগত প্রতিযোগিতা তো আর গায়েব হয়ে যায়নি, কেউ নিজের স্বার্থে গোষ্ঠীর ভারসম্যতা নষ্ট করতেই পারে। ধরুন, দশজনের একজন প্রতারণা করলো। বেশি খাবার পাওয়ার লোভে বা অন্য কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য খাদ্য চুরি, সহযোগীর উপর আক্রমণ বা হত্যাকাণ্ডের মতো কিছু ঘটালো। তাহলে ঐ প্রতারকের উপর গোষ্ঠীর আর কারও ভরসা থাকলো না। এই যে একজনের কর্মকান্ডের জন্য গোষ্ঠীর বাকী সদস্যদের ক্ষতির সম্ভবনা আছে এটা গোষ্ঠীর জন্য একটা হুমকি, এটা গোষ্ঠীর টিকে থাকার সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। যাহোক, আবার আমরা ধর্ষণের বিষয়ে ফিরে তাকাই। একটু আগেই বললাম, যৌন জননের জন্য নিন্ম শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। কাপুচিন মানকি, শিম্পাঞ্জি, পেঙ্গুইনদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি কিংবা বহুগামীতা বিষয়টা দেখা যায়। পুরুষের বহুগামীতা এখনো মানবসমাজে সরাসরিই বহুল পরিসরে দেখতে পাই আমরা। আমাদের প্রাচীন সমাজেও এই বহুগামিতা ছিলো। তবে সেটা পুরুষদের মধ্যে যতটা বেশি, নারীদের মধ্যে তুলনামুলক কম। কারণ, যৌন জননের কারণ যা-ই হোক ফলাফল ছিলো বাচ্চা উৎপাদন, জিনের প্রবাহ বজায় থাকা। একজন মেয়ে বছরে সর্বোচ্চ একবার গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে। তাই প্রজননের জন্য তার বহু পুরুষের প্রতি আকর্ষণও কম। কিন্তু একজন পুরুষ? সম্ভব হলে বছরে ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ জন আলাদা আলাদা নারীর সাথে সহবাস করে প্রজনন ঘটায়। তাই পুরুষের মাঝে বহুগামিতা বেশি, তারা জিনগত আচরণই এটা, তারা সহজেই যে কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং বহুবিবাহ, পরকীয়া তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।
বহুগামিতা বহু বাচ্চা উৎপাদনের পথ খুলে দিলেও এতে উৎপাদিত সন্তানের মৃত্যুহার ছিলো অত্যন্ত বেশি। ফলে নিন্মশ্রেণীর প্রাণী যাদের একইসাথে অনেকগুলো সন্তান হয় কিংবা ঘন ঘন প্রজনন ঘটে তাদের ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধা না হলেও মানুষের মতো প্রাণী যাদের বছরে সর্বোচ্চ এক দুইটা বাচ্চা জন্ম নেয় তাদের ক্ষেত্রে এই মৃত্যুহার অনেক বড় প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে প্রকৃতিতে অভিযোজিত হয় প্যারেন্টাল কেয়ার। প্যারেন্টাল কেয়ার বহু প্রাণীতেই দেখা যায়। এই পিতৃমাতৃজনিত মমতা গড়ে নারীর মধ্যে সর্বদা বেশি। ডিম্বাণু উৎপাদন থেকে শুরু করে গর্ভধারণ- সবকিছুতে নারীর শক্তিখরচ পুরুষ অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি। ফলে নিজের সন্তানকে টিকিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা এবং আকাঙ্ক্ষা তার ভিতরেই অধিক দেখা যায়। পুরুষ কোনো নারীর সাথে সহবাস করে একটা বাচ্চা জন্ম দিলো, ঐ বাচ্চার জিনগত মিল অবশ্যই প্রজাতির আর কোনো সদস্যের তুলনায় ঐ পুরুষের সাথেই বেশি। তাই স্বভাববশতঃ ঐ বাচ্চার প্রতি ঐ পুরুষের একটা অন্যরকম টান থাকবে। ঐ বাচ্চার কোনো অসুবিধা হলে, খাদ্যাভাব দেখা দিলে ঐ পুরুষ ছুটে আসতো সহায়তার জন্য। এভাবে পিতা-মাতা-সন্তানের মাঝে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যেটা শুধু বাচ্চা উৎপাদন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনা, তাকে রক্ষা এবং বড় করা অবদি বিস্তৃত হয়। এছাড়া পিতা-মাতার মধ্যে সেক্সুয়াল লাভের বিষয়টাতো আছেই।
আস্তে আস্তে দেখা গেলো একজন পুরুষের দশজায়গায় দশজন সন্তান। ঐ পুরুষের দশজনের প্রতি সমানভাবে খেয়াল রাখা অসম্ভব বিষয়। ফলে আস্তে আস্তে বহুগামিতা ছেড়ে একগামিতায় ঝোঁকা শুরু করে তারা। বিবর্তনের ভাষায়, বাচ্চার পিতা-মাতার সেক্সুয়াল লাভ, সন্তানদের সঠিক পরিচর্যা, যত্নের মাধ্যমে বড় করে প্রজনন উপযোগী করা- এই পদ্ধতিতে নিজের স্থায়ী প্রতিরূপ টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবু একেবারেই বহুগামিতা গেলো না গোষ্ঠী থেকে। বরং একজন পুরুষ তিন-চারজন বা তার বেশি স্ত্রী নিয়ে পরিবার গড়ে তুললো। নারীদেরও অনেক সুবিধা হলো। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তারা বাচ্চা সামলাবে নাকি শিকার করবে নাকি নিজেদের রক্ষা করবে নাকি অন্য কাজ গোছাবে? গোষ্ঠী ব্যবস্থায় যদিও এর কিছুটা সমাধান ছিলো, কিন্তু পুরো সমাধানটা ছিলো না। ধরুন, আপনি কোনো যৌন সুবিধা পাননি একজন নারী হতে, সে আপনার গোষ্ঠীর হলেও আপনি কেনো তার সন্তান এবং তার এত দায়িত্ব নিবেন? বরং আপনার নিজের যেসকল নারীর সাথে সম্পর্ক আছে, আপনি যত্ন নিলে তাদের নিবেন, তাদের সুরক্ষায় থাকবেন (এই যে যৌনতার টান, একজনের প্রতি হিংসার মনোভাব আরেকজনের প্রতি ভালোবাসা)। এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে অগোছালো গোষ্ঠীব্যবস্থাকে একটা পরিবার-ভিত্তিক গোষ্ঠীব্যবস্থায় রূপান্তর করতে সক্ষম হলো। নিজেই ভেবে দেখুন- নারীদের সুরক্ষা, বাচ্চার সুরক্ষা, পুরুষদের যৌন চাহিদা, সবার খাদ্য চাহিদা, পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টিকে থাকার মতো যেসব সমস্যা ছিলো তা এই পরিবার ব্যবস্থা আসার ফলে সমাধান হয়ে গেলো।
দিন গেলো, রাত গেলো- পরিবার ব্যবস্থা সুগঠিত হলো। আস্তে আস্তে নারী-পুরুষের একে উপরের প্রতি বিশ্বস্ততা বাড়লো। এবার আবার অতীতে ফিরি, আরও অতীতে, যখন সেক্সের উপর ভিত্তি করে ভালোবাসার উৎপত্তি হয়নি। কিন্তু উৎপত্তি ঘটেছে ধর্ষণের। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, ধর্ষণের। ধর্ষণ অনেক আগেই প্রকৃতিতে এসেছে। কেনো এসেছে? কারণ, সন্তান উৎপন্ন হলেই হলো, সেটা নারীর অনুমতিতে হোক বা না হোক, জিনের প্রবাহ তো ঘটে। কিন্তু ধর্ষণের উৎপত্তির পর হতে মানবসমাজের আগমন পর্যন্ত লক্ষবছর বিবর্তন ঘটেছে আমাদের পুর্বপুরুষদের মনস্তত্ত্বে, এটাকে আমরা বলে থাকি কগনিটিভ বিবর্তন। এই বিবর্তনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি, একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী, একই গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সদস্য স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা শিখে, নতুন পরিস্থিতি হতে শিক্ষা নেয়, এই শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটার কৌশল আবিষ্কার করে, ফলে একই আচরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই কগনিটিভ বিবর্তনই দায়ী ধর্ষণের কারণ বহুমাত্রিক করে তুলতে।
→ প্রথম কারণটা ধর্ষণের থেকে বেশি দায়ী অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন নিপীড়নের। আমাদের সমাজের মেয়েরা নিজেদের তারুণ্যে, কৈশোরে অনেক সময় বাল্যবয়সে নিজের পরিবারেরই সদস্য কিংবা পরিচিতজনদের (কাজিন, পারিবারিক বন্ধু, পিতৃসম কাকা, চাচা, মামা প্রভৃতি) দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এই ধরনের নিপীড়ন বেশি হয় যৌন হতাশা আর লালসা থেকে- বাল্যবয়সে বাঁধাপ্রদানের কিংবা প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই, সহজেই মনের তাড়না মিটানো যায়। এজন্য অনেকেই যৌনসঙ্গী না পাওয়ার হতাশা কিংবা যৌনসঙ্গী থাকার পরেও (বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটা বেশি) তৃপ্ত না হওয়ার হতাশা দূর করে এরকম সহজলভ্য কিশোরী, শিশু, বালিকা নিপীড়নের মাধ্যমে। আরও একটা কারণ রয়েছে পরিচিতজনদের দ্বারা এরকম নারীদের নিপীড়িত হওয়ার- বিভিন্ন ধরনের পর্ণোগ্রাফি যেখানে বৌদি, শ্যালিকা, কাজিন, বান্ধবীদের যৌনসঙ্গী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে তরুণ থেকে যুবক- অনেকের মনেই নিজের পরিবারের কিছু সদস্যদের থেকে যৌনসুখ প্রাপ্তির আশা সৃষ্টি হয়। ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ঘটনা।
→ বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের সময় ভিকারুননিসার বাচ্চা মেয়েরা যখন আন্দোলন করছিলো বৈষম্যের বিরুদ্ধে তখন ছাত্রলীগের (বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল) একজন প্রাক্তন নেত্রী পোস্ট দিলো, ‘তোমাদেরকে রেইপ করবে আমার সোনার ভাইয়েরা ‘। এই ভদ্রমহিলার এই উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ষণের বহুমাত্রিক-মনস্তত্ত্বের খানিকটা বুঝতে গেলে। ইনি পুরুষ নন, ইনি কোনো আন্দোলনকারীর পোশাক দেখে উত্তেজিত হননি, এনার কাছে ধর্ষণ হচ্ছে মেয়েদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার একটা মোক্ষম অস্ত্র। এই ধরনের ধর্ষণ যে শুধু হুমকিতে আটকে থাকে এমন কিন্তু না, বহু ধর্ষণের কেইস ঘাটলে দেখা যাবে সেগুলো কোনো যৌন আকর্ষণ থেকে হচ্ছে না, হচ্ছে রাজনৈতিক শত্রুতা থেকে বিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য। এবং জেন্ডার ও এখানে ইস্যু না। ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছেন একজন মহিলা৷ ঠিক এই একই ঘটনার বিপরীত প্রতিরূপও রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওইসময়ে ঢাবির ছাত্রলীগের নেত্রীদের পোস্টের কমেন্টবক্সগুলো। প্রচুর মুক্তিকামী ছাত্রজনতা এই নারীদের ধর্ষণ করতে চায়, কারণ এই নেত্রীরা তৎকালীন সরকারের পক্ষশক্তি। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, সাদ্দাম-ইনানও কিন্তু পক্ষশক্তি ছিলো, কিন্তু তাদেরকে জনতা পেটাতে চাচ্ছে, হাত-পা ভেঙে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু আতিকা বা তিলোত্তমাকে জনতার কেউ কেউ রেইপ করতে চায়। অর্থাৎ নারীকে বিচার করার মোক্ষম উপায় জনগণের কাছে পেটানো বা আদালত না, বরং নারীর বিচারের উপায় হচ্ছে তাদেরকে ধর্ষণ। এখানের এই জনতার ‘কেউ কেউ’ কিন্তু ভালোমানুষ, তবু তাদের কাছে রেইপ একটি টুল। বিচারিক টুল। একটি মেয়ের প্রতি আপনি প্রতিশোধপরায়ণ। একইসাথে একটি ছেলের প্রতি আপনি প্রতিশোধপরায়ণ। ছেলেটিকে আপনি মেরে হাড্ডিগুডি ভেঙে হাসপাতালে ঝুলায়ে দিতে চান এর জন্য, কিন্তু মেয়েটিকে চান ধর্ষণ করতে। বিপক্ষ নারী হলে তাকে দমন করার, প্রতিশোধ নেওয়ার মোক্ষম উপায় আপনার কাছে ধর্ষণ। এই প্রতিশোধের আরেকটা বড় উদাহরণ প্রেমে ব্যর্থ হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়া। কেউ আপনাকে না বললো? আপনি তাকে এত পছন্দ করেন, তাকে “ভালোবাসেন”, তারপরও সে কীভাবে আপনাকে প্রত্যাখান করলো? সে আপনার না হলে আর কারও হবেনা। এই প্রতিশোধপূর্ণ মনোভাবও ধর্ষণের অন্যতম কারণ।
→ আপনি একজন ছাপড়ি। হাসপাতালের ওয়ার্ড বয়। আপনি যে হাসপাতালে কাজ করেন সেখানে প্রচুর সুন্দরী ডাক্তার কাজ করে। এদেরকে আপনার ভালো লাগে। এজন্য ভালো লাগে না যে, ওরা ছোটো ছোটো কাপড়চোপড় পরে। আপনি জানেন এদের আপনি কখনোই নিজের সঙ্গী হিসেবে পাবেন না। আপনার মধ্যে একধরণের আকাশকুসুম কল্পনা কাজ করে। এই কল্পনার একটা অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে শ্রেণীবৈষম্য। আপনি অনেক জনপ্রিয় মডেল কিংবা নায়িকা নিয়ে এরকম কল্পনার দুনিয়া বানাতে পছন্দ করেন একই কারণে। এই যে হাসপাতালের একজন ডাক্তার আপনার তুলনায় বড়লোক এবং শিক্ষিত হওয়ায় একটা শ্রেণীবৈষম্য কাজ করছে, সেটার জেরে কোনোদিন তাই সুযোগ পেলে তাকে ধর্ষণ করে ফেললেন। শ্রেণিবৈষম্য ভেঙে দিলেন, এক ধরনের অন্যরকম প্রাপ্তির সন্তুষ্টি আসলো আপনার মাঝে। এই যে নারী যাই করুক, যত পড়াশোনাই করে ফেলুক, উপরেই উঠে যাক, শুধুমাত্র একজন পুরুষ হবার দরুণ আপনার একটা মোক্ষম সুযোগ রয়েছে তাকে টেনে মাটিতে এনে ফেলবার — এটা আপনি জানেন মনে মনে বিশ্বাস করেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন এটাকে বাস্তবায়ন করার, এটাই কালচারাল সাইকোলজিই ধর্ষণের মানসিকতাকে উশকে দেয়, নারীদের পোশাকে তখন কিছুই যায় আসেনা। নারীর সমস্ত অর্জন আর স্বাধীনতাকে আপনি এক তুড়িতেই গুঁড়িয়ে দিতে পারেন, এই ক্ষমতা আপনার আছে সে আপনি হন না কেন একটা রাজমিস্ত্রী, শ্রমিক, রিকশাচালক, চাকুরিজীবী, বিজনেসম্যান, শিক্ষক যা খুশি।
→ যুদ্ধের সময় ধর্ষণ কিংবা ডাকাতির সময়ে ধর্ষণের পিছনে আবার অন্যরকম মনস্তত্ত্ব কাজ করে। এই ধর্ষণের প্রথম লক্ষ্য- ত্রাস সৃষ্টি করা। আপনি একজনকে হত্যা করলে সেই পরিমাণ ত্রাস সৃষ্টি করতে পারবেন না যতটা একজনকে ধর্ষণের মাধ্যমে করা যায়। এই যে সম্প্রতি রাজশাহীর বাসে ডাকাত কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা তুমুল আলোচিত হলো, এর কারণও একই। কোনো যুদ্ধে আপনি যখন কোনো সৈনিককে অত্যাচার করবেন আর দশজন সৈনিক যতটা না ভয় পাবে তার থেকে বেশি ভয়, ত্রাস সৃষ্টি হবে আমি যখন সৈনিকদের পরাজিত করার পরে বা আগে তাদের কাছের নারীদের ধর্ষণ করবেন। বাকীরা তখন নিজের পরিবার আপনজনের সুরক্ষার জন্য মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন থাকবে, অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই তাদের পরিবার নিয়ে পলায়ন করবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য- শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি কোনো যুদ্ধে বিপক্ষ গোষ্ঠীর পরিচয় মুছে দেওয়া, যে লক্ষ্যে একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশী নারীদের অবাধে ধর্ষণ আর নির্যাতন করেছিলো। আবার যুদ্ধশেষে যুদ্ধবন্দীদের ভোগ করা, ধর্ষণ করা যুদ্ধজয় প্রকাশের নিমিত্ত মাত্র। এখানে ধর্ষণ কাজ করে জয়ীদের “সাকসেস পার্টি” হিসেবে। তাদের কাছে এই যুদ্ধবন্দীরা লুট করা দশটা বস্তুর মতোই, এদের সাথে যা খুশি করা যায়, এরা অর্জন করার বিনোদনের উপহারমাত্র প্রাণী ব্যতীত আর কিছুই নয়।
→ পশ্চিমবাংলার বহুল আলোচিত ধর্ষণের ঘটনা আরজি করের মৌমিতা দেবনাথ ধর্ষণ কেইস। এই এক ঘটনা সমগ্র ভারত এবং ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও বিক্ষোভের ঝড় তুলেছিলো। মৌমিতা কেনো ধর্ষিত হয়েছিলো? এর ঠিক কোনো উত্তর নেই। অনেক সন্দেহ রয়েছে, মৌমিতার মৃত্যুর পর হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিলো মৌমিতা আত্মহত্যা করেছেন। মৌমিতার সাথে হাসপাতালের বিভিন্ন অন্তঃকন্দলের খবরও সামনে আসছিলো। ‘হাসপাতালের কেউ’ হিসেবে তাঁদের সন্দেহের তালিকায় চারজন জুনিয়র ডাক্তার আছেন বলে জানিয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা। তার ভাষ্যমতে ‘ধর্ষনের দিন রাতের বেলা (৮ আগস্ট রাতে) যারা আমার মেয়ের সঙ্গে ছিল, তাদের আমরা প্রচণ্ড-প্রচণ্ডভাবে সাসপেক্ট (সন্দেহ) করছি। ডিএনএ রিপোর্ট তো পাওয়া গিয়েছে। তথ্যপ্রমাণ দেখেছেন। কোনও মহিলারও উপস্থিতি আছে।” যাহোক এই কেইসের পুরো রহস্যোদ্ধার পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় আসলে ঠিক কোন কারণে ১৫-১৬ জন মিলে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছিলো মৌমিতাকে। হয়তো কোনো কিছু পূর্বশত্রুতা ও রেশারেশি, হয়তো মৌমিতা এমন কিছু জানতো যেটা তাদের অপকর্মর জন্য ক্ষতিকর ছিলো- যেটাই হোক না কেনো মৌমিতার ক্ষেত্রেও ওই ‘প্রতিশোধ আর দমনর অস্ত্র’ হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। কোনো যৌন টান কিংবা ছোট পোশাকের জন্য না।
→ সবশেষে একসাথে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলাপ করবো। নারীরা নিজের পিতা দ্বারাও ধর্ষিত পারে, এমন বহু ডকুমেন্টেড কেইস রয়েছে। বহুল আলোচিত একটা কেইস অস্ট্রিয়ার জোসেফ ফ্রিটজ। ২৪ বছর ধরে নিজের মেয়ে এলিজাবেথ ফ্রিটজকে এই ব্যক্তি ধর্ষণ করে যার ফলে ৭ সন্তানেরও জন্ম হয়। রিপোর্ট অনুসারে জোসেফ ১১ বছর বয়সেই এলিজাবেথকে যৌন নিপীড়ন করা শুরু করেছিলো। পরবর্তীতে জোসেফের আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। আমরা ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ধর্ষণেরও ঘটনা দেখতে পাই। এই ধর্ষণের পিছনে কিছুক্ষেত্রে কাজ করে ‘পেডোফেলিক ডিজঅর্ডার’ যেখানে ধর্ষক শিশুদের সাথে বিভিন্ন যৌনআচরণে লিপ্ত হতে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে। এই শিশু ধর্ষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মকান্ড নিয়ে অনুতপ্ত তো হনই না, বরং তারা শিকারদের মুখ বন্ধ করে রাখেন ভয় দেখিয়ে। এদের ভিতর এমপ্যাথির অভাব থাকে, এরা শিশুর কষ্টে, ব্যথা বেদনায় তৃপ্তি লাভ করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা একবার এগুলো করে থেমে থাকেনা। বারবার এগুলো করতেই থাকে, বিভিন্নজনের সাথে।
→ একটা কেইস এবার আপনাদের চিন্তা করার জন্য রেখে যাই। এইতো গতবছর ডিসেম্বরে জার্মানিতে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ সবার সামনে প্রকাশ্যে আসে। প্রায় ৭০,০০০ সদস্যের গ্রুপ যেখানে সবাই আড্ডা দিতো কীভাবে নিজের ঘরের নারীদের যৌন নির্যাতন করা যায়। নিজের মা, বোন, স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তারা নিয়মিত যৌন নিপীড়ন করতো এবং নিপিড়ন করার নতুন নতুন পরিকল্পনা দিতো অন্যদের। এই গ্রুপেরই একজন ছিলো ডমিনিক পেলিকোট যে নিজের স্ত্রীকে নিয়মিত ঘুম ও নেশাজাতীয় ওষুধ দিয়ে অচেতন করে অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিতো তাকে ধর্ষণ করার জন্য। এভাবে নিজের অজান্তেই প্রায় ৫০ জনের দ্বারা ধর্ষিত হয় পেলিকোটের স্ত্রী। এই যে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ এতে একজন দুজন না, প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ৫০ জন এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে এসব নিয়ে আড্ডা এবং ছোটোখাটো কুকর্মে লিপ্ত প্রায় ৭০ হাজার জন পুরুষ, এরা নারীর পোশাক দেখে উত্তেজিত হয়ে এমন করেছে? এই ধরনের কেইসে পুরুষের কোন মনস্তত্ত্ব কাজ করছে বলে আপনাদের মনে হয়? নাকি এটাও নারীদেরই দোষ বলে গণ্য হবে আপনাদের কাছে?
এই যে আপনি কোনো নারীর প্রতি রাগন্বিত হলে তাকে ধর্ষণ করতে চান, কোনো নারীকে পছন্দ হলে তাকে জোর করে পেতে চান, প্রতিশোধ নিতে চাইলে তাকে ধর্ষণ করতে চান, রাজনৈতিক মতবাদ না মিললে ধর্ষণ করতে চান, সে আপনার থেকে উঁচু ক্লাসের কিংবা বড়লোক বলে ধর্ষণ করতে চান —অর্থাৎ আপনি জানেন ও মানেন যে একজন নারীর সাজানো গোছানো সবকিছু নিমিষে গুড়িয়ে দেওয়ার সবথেকে সহজ উপায় হচ্ছে তাকে ধর্ষণ করে ফেলা। এমনকি আপনি ফেসবুকে ফারজানা সিঁথির মতো ইনফ্লুয়েন্সারদের গালি দেন “এই মেয়েকে তো কেউ ধর্ষণও করবেনা”, আপনার মনস্তত্ত্বে ধর্ষণকে এমন একটা টুল হিসেবে অভিযোজিত হয়ে চলেছে যেখানে এখন আপনি ধর্ষণকে অপরাধ বলেও ভাবতেছেন না, বরং এমনভাবে প্রমোট করতেছেন উল্লিখিত বাক্যাংশে যেনো ধর্ষিত হওয়াটা একটা পুরষ্কার। আপনি হয়তো সত্যিকারের জীবনে কাউকে ধর্ষণ করছেন না কিন্তু আপনার কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আপনি মনে করেন সিঁথি কিংবা তিলোত্তমার মতো মেয়েদের ধর্ষিত হওয়াই উচিত, তারা ধর্ষিত হলে আপনি খুশি হন। আপনিই এই মনোভাব গড়ে তুলছেন, এটাকে ব্যবহার করার জন্য, আবার কেউ ধর্ষিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হারকিউলিসকে চাচ্ছেন ধর্ষককে শাস্তি দেওয়ার জন্য- শাস্তি আপনার কম প্রাপ্য?
আপনি কতটা বেহায়া ভেবে দেখুন, একদিকে যেমন ধর্ষণের মনস্তত্ত্বকে আপনি নরমালাইজ করে চলেছেন অন্যদিকে জ্ঞানীর মতো সমস্ত দোষ নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটা অজুহাত খুঁজে পেয়েছেন- নারীর পোশাক। ধর্মীয় সংস্কৃতিতে নারীর পোশাকের যে আদেশ সেগুলো ব্যবহার করে সবাইকে বুঝানোর প্রচেষ্টায় রয়েছেন ধর্ষণের জন্য পোশাক দায়ী। এক ঢিলে দুই পাখি, নির্যাতিতও হলো আবার দোষও নির্যাতিতার হলো। বছর বছর ধরে এই একটা অপরাধকে, এই অপরাধের মনস্তত্বকে পুরুষমহলে বৈধতা দিয়ে চলেছেন আবার যেকোনো ধর্ষণ হলে বলছেন, ‘কাপড় ছোটো’, এসব দুমুখো কর্ম থেকে বিরত থাকুন। অপরাধকে অপরাধ বলতে শিখার মতো মানসিকভাবে সৎ অন্তত হন। বহু আগে, একজন বিখ্যাত লেখক বিজ্ঞানের উপর আঙুল তুলতে গিয়ে বলেছিলেন, কোন কর্মকাণ্ড অপরাধ, কোন কর্মকাণ্ড অপরাধ নয় এটা বলার সক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, বিজ্ঞান কীভাবে ব্যাখা করতে পারে ধর্ষণের মতো কর্মকাণ্ড অপরাধ কিনা?
যৌনতার নির্বাচনে সঙ্গী পাওয়ার জন্য বা প্রজনন ঘটানোর জন্য একজন পুরুষ তার সামর্থ্য প্রমাণ করে নারীর সামনে, নারী যদি ওই পুরুষের শক্তি, সামর্থ্য দেখে মুগ্ধ হয় তবে সে রাজী হয় তার সাথে থাকতে। এটা শুধু মানবসমাজে হচ্ছে এমন না, মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী সকল পর্বের বহু বহু প্রজাতিতেই এই যৌনতার নির্বাচন দেখা যায় যেখানে পুরুষ নিজেকে নারীর উপযোগী হিসেবে প্রমাণ করে। ফলে যেটা হয়, সুস্থ সবল জিন (রোগ জরা মুক্ত, ভালো বৈশিষ্ট্য ও গুণযুক্ত জিন) বলে যেটাকে অভিহিত করা যায় সেটাই পরবর্তী বংশে অতিবাহিত হয়। কিন্তু ধর্ষণে নারীর সম্মতি নেওয়া হয়না, যার ফলে ধর্ষণের মাধ্যমে প্রজনন ঘটলে পরবর্তী প্রজন্মে অপেক্ষাকৃত নিম্নগুণ সন্তান জন্ম নিবে (যদিও মানুষের ক্ষেত্রে গুণাগুণ নির্ধারণে সন্তানের পরিচর্যা অনেক বড় ভূমিকা রাখে, আমরা সমগ্র প্রাণীজগত বিবেচনায় এখানে যুক্তি বিশ্লেষণ করছি)। এর ফলাফল হিসেবে ঐ প্রজাতির টিকে থাকার উপযুক্ততা তথা ইনক্লুসিভ ফিটনেস কমে যাবে। এর বাস্তব প্রমাণও রয়েছে। টিকে থাকার ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যেসব সন্তান নারীর সম্মতিতে হওয়া প্রজননের মাধ্যমে ঘটে তাদের সার্ভাইভাল রেট বেশি আর যেমনটা আগে বলেছি, সম্মতি ছাড়া হওয়া প্রজননে সার্ভাইভাল রেট কম। এছাড়া ধর্ষণের ফলে নারীর শরীরে খারাপ প্রভাব পড়ে। তাদের জেনেটিলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পরবর্তীতে তাদের যৌন জননের উপর প্রভাব ফেলে। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে ধর্ষণ নারীর জন্য একটা ট্রমা হিসেবে থেকে যায়। ধর্ষণের সময় অনেকক্ষেত্রে পুরুষ এতটা হিংস্র হয়ে ওঠে যে সে নারী প্রাণীর সাথে থাকা সন্তানদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না, এই হিংস্রতা প্রজাতির টিকে থাকার পথে অনেক বড় বাঁধা তৈরি করে। তাহলে বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ চরম ক্ষতিকর এবং প্রতিবন্ধক কোনো প্রজাতির সামগ্রিকভাবে টিকে থাকার জন্য যদিও এটা বিবর্তনেরই উপজাত।
আমরা এবার শুধু আমাদের মানবসমাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারি। ভাবুন, একজন ধর্ষকের বোন বা প্রেমিকা ধর্ষিত হলে তার কেমন অনুভব হবে? হ্যাঁ, তারও ঠিক ততটাই রাগ, দুঃখ, কষ্ট হবে। ধর্ষণের পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ কীভাবে কাজ করে তা তো পুরো প্রবন্ধ জুড়েই জানলাম আমরা, এবার ভাবুন পরিচিত কেউ বা অপরিচিত কারও ধর্ষনের কথা শুনলে আমাদের কেনো কষ্ট হয়, আমাদের কেনো অস্বস্তি লাগে? এই অনুভূতিটা আমাদের মাঝে দৃঢ় হয়েছে পরিবার ব্যবস্থা এসে। ঐ যে স্ত্রীর প্রতি সেক্সুয়াল লাভ, দায়িত্ববোধ, বোনের প্রতি ভালোবাসা, বান্ধবীদের নিরাপত্তাবোধ, সামাজিক দায়িত্ব। এসবই আমাদের মাঝে তীব্র করেছে ধর্ষণবিরোধী চেতনা। নারীর অনুমতি ছাড়া জোর করে তাদের সাথে সহবাস হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতার, পরিবার-পরিবার কিংবা কিংবা ব্যাক্তি-ব্যাক্তির সংঘর্ষের কারণ। সাথে সাথে ধর্ষিতার মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্যের অবনতি তো আছেই। আর তাই ধর্ষণ বিবেচিত হওয়া শুরু হয়েছে অপরাধ হিসেবে। ধর্ষককে কেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শাস্তি দিতে হবে? যেসকল কর্মকান্ড কোনো গোষ্ঠীর টিকে থাকার ফিটনেস কমে, অন্তঃকোন্দলের জন্ম হয় সেসকল কর্মকাণ্ড অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, সেগুলো দমন করতে হবে। প্রায় সকল গোষ্ঠীতে মোটা দাগে একইধরনের কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এই কারণেই (কিছু ব্যতিক্রম রয়েছেই)। যেহেতু টিকে থাকার জন্য সর্বোচ্চ ফিটনেস বজায় রাখা বাঞ্চনীয় তাই ধর্ষণের মতো কর্মকান্ডে বিনাবাক্যে শাস্তি দেওয়া বাঞ্চনীয়। এই ধরনের মনস্তত্ত্বধারীদেরও সম্ভব হলে সবখানে দমন করা উচিত।
লেখক: সাজিদ বিন আজাদ, তিকতালিকীয় সদস্যবৃন্দ
সম্পাদনা ও কপিরাইট: তিকতালিক-Tiktaalik