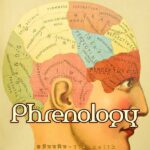পানির স্তরায়ন (water stratification) বলতে এমন সব ঘটনাকে নির্দেশ করা হয় যেখানে একই জলাধারের মধ্যে পানির ভিন্ন ভিন্ন স্তর সৃষ্টি হতে পারে কিংবা দুইটি ভিন্ন জলাধারের পানি এমনভাবে মিলিত হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে যেনো পর্যবেক্ষকের নিকট মনে হয় তারা একে অপরের সাথে কোনো অজানা কারণে মিশে যাচ্ছে না। এমন স্তরায়ণ হওয়ার গল্প আমরা শুনেছি, হয়তো ইন্টারনেটের বদৌলতে আমরা দেখেছিও! বাংলাদেশের চাঁদপুরে তিন নদীর মোহনাতে এরকম হতে দেখা যায়; যেখানে পদ্মা, মেঘনা এবং ডাকাতিয়া নদীত্রয় এসে মিশেছে ঠিকই কিন্তু এদের পানি ঠিকমতো একে অপরের সাথে মিশেনা, খালি চোখেই স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায় কোনপাশে কোন নদীর পানি! ভারতের নবদ্বীপের পাশে গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীর মিলনস্থানেও একইরম ঘটনাই ঘটে। ঠিক যেমন ভূমিতে পাশাপাশি দুই দেশের মাঝে কাঁটাতারের প্রাচীর থাকে, এসব নদীর মিলনস্থলের পানিতেও যেনো ঠিক একইরকম সীমানা নির্দেশক প্রাচীর দৃশ্যমান।
এসব ঘরের পাশের ছোটোখাটো উদাহরণ বাদ দিই। সুবিখ্যাত প্রশান্ত মহাসাগর এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগর নিয়েও এইরকম গল্পকথা জীবনে একবার হলেও শোনা হয়েছে না? জলাধারের জগতের সবচেয়ে বড় দুই মহারথীর পানি কখনো একে অপরের সাথে মিশে না। এই নিয়ে ভার্চুয়াল জগতে রয়েছে বহু বহু ভিডিও। এমনই ২০১৫ সালে শ্যুট করা এক ভিডিও এখনো অনলাইন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হতে দেখা যায় যেখানে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের পানির মধ্যে কাঁটাতারের সীমানা নির্ধারণী প্রাচীর দৃশ্যমান। দেখে মনে হবে- এ দুই তরল আসলে পানি না, একটা পানি আরেকটা পানির মতোই অন্যকোনো দ্রবণ যারা কখনোই পরস্পরের সাথে মিশবে না। কিন্তু ২০১৫ এর ভিডিওটা আসলে ভুয়া, ভিডিওটা মোটেও এই দুই মহাসাগরের নয়। এই ভিডিও আলাস্কার বরফ গলা বিশুদ্ধ স্বচ্ছ পানির সাথে মহাসমুদ্রের পানির মিলনের। সমুদ্রের অতিরিক্ত লবণযুক্ত ঘন পানি স্বচ্ছ পানির সাথে সরাসরি মিশতে পারেনা বলে এমন বিভেদতলের সৃষ্টি হয়।
শুধু প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগর নিয়ে নয়; দুই পানির স্তরের মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর, প্রাচীরের দরুণ পানির না মেশার গল্প শোনা যায় ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক নিয়েও। এই গল্প বাঙালীদের মাঝে বেশি শুনতে পাওয়ার পিছনে একটা ছোটো ধর্মীয় কারণও রয়েছে। মুসলিম অ্যাপোলজিস্ট আই. এ. ইব্রাহীম তার বই, “আ ব্রিফ ইলাস্ট্রেটেড গাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম” এ ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিকের দাবিটি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ভূমধ্যসাগরের পানি আটলান্টিকের সাথে এক ফোঁটা না মিশে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়েই কয়েকশত মাইল প্রবাহিত হয়েছে প্রায় ১০০০ মিটার গভীরতা জুড়ে।” অর্থাৎ, ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিকের মধ্যে এমন এক অদৃশ্য অন্তরালের সৃষ্টি হয়েছে যে এরা পাশাপাশি একই সাথে প্রবাহিত হলেও দুই সাগরের পানিতে কোনো মিশ্রণ ঘটছে না। আই. এ. ইব্রাহীম সাহেবের বই থেকেই আস্তে আস্তে বিষয়টা আমাদের দেশের ধর্ম প্রচারকদের নিকট জনপ্রিয় হয় এবং তাদের ওয়াজ-মাহফিলের বদৌলতেই এটা অনলাইনে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। জনাব আই. এ. ইব্রাহীম মূলত নিজের বইতে মেডিটেরানিয়ান আউটফ্লো এর কথা বুঝিয়েছিলেন। মেডিটেরানিয়ান আউটফ্লো জিনিসটা কী? আসলেই কি সম্ভব যে পানির ভিতর দিয়ে পানি যাবে কিন্তু পরস্পরের সাথে মিশবে না? এই মেডিটেরিয়ান আউটফ্লো এর পিছনে থাকা সত্যতা ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের এই লেখাটা শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে আপনাদের।
প্রশান্ত-আটলান্টিক, ভূমধ্যসাগর-আটলান্টিক কিংবা যেকোনো দুই জলাধারের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখতে পাওয়া বিভেদতলের মতো এত স্পষ্ট অন্তরাল বাস্তবে তৈরী না হলেও স্তরায়ন ঠিকই ঘটে। এরকম স্তরায়ণ ঘটার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে ভিন্ন ভিন্ন পানির ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা। কোনো জলাধারের পানির যেকোনো একটা অংশকে যদি আমরা সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করি তবে এর উপর দুইটা বল কাজ করে, এক হলো ওই সিস্টেমের ওজন (W) এবং সিস্টেমের প্লবতা (F)। জলাধারের কোনো অঞ্চলের পানির ঘনত্ব আশেপাশের অঞ্চল হতে বেশি হলে উক্ত প্রথম অঞ্চলের পানির ভর তথা ওজনও বেশিই হবে তুলনামূলকভাবে। ওজন এবং প্লবতার লব্ধি কাজ করবে কোনদিকে তা নির্ভর করে কোনটার মান বেশি তার উপর।
যদি পুরো জলাধারের উক্ত ভারী অঞ্চলের ঘনত্ব ρ’ ধরি তবে উক্ত অঞ্চলের পানির ওজন W = উক্ত অঞ্চলের পানির আয়তন (V) × পানির ঘনত্ব (ρ’) × অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) = পানির ভর (m) × অভিকর্ষজ ত্বরণ (g), এই ওজন কাজ করে নিচের দিকে। ভারী অঞ্চল ব্যতীত আশেপাশের পানির গড় ঘনত্ব ρ হলে ভারী অঞ্চলের পানির প্লবতা হবে F = Vρg, এই প্লবতা কাজ করে উপরের দিকে। যেহেতু ρ’ > ρ, সেহেতু W > F এবং ওজন-প্লবতার লব্ধিও নিচের দিকেই কাজ করবে। আবার, কোনো অংশের ঘনত্ব আশেপাশের অংশ থেকে কম হলে উক্ত অংশের ভর তথা ওজনও কম হবে তুলনামূলক। ওজন এবং প্লবতার লব্ধি কাজ করবে উপরের দিকে। ফলে দেখা যাবে, একই আয়তনের দুটি ভিন্ন অংশের মধ্যে যার ঘনত্ব যত বেশি সে অংশ তত নিচের দিকে ওজনের চাপে যাবে, অপরদিকে কম ঘনত্বের অংশ উঠবে উপরে, প্লবতার দিকে। এভাবে স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে যাবে পানি।
সমুদ্রের পানির এই ঘনত্ব নির্ভর করে আরও তিনটি বিষয়ের উপরে।
i) পানির লবণাক্ততা (Salinity)
ii) তাপমাত্রা (Temperature) এবং
iii) চাপ (Pressure)
যেকোনো প্রবাহী পদার্থকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। সংকোচনযোগ্য (Compressible) প্রবাহী কিংবা অসংকোচনযোগ্য (Incompressible) প্রবাহী। এবার চিন্তা করুন। এক বোতলভর্তি বাতাসে জোরে চাপ দিলে তার ভিতরে কিন্তু আরও বাতাস রাখার জায়গা সৃষ্টি হবে, কারণ বাতাসের দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অণুগুলো তখন কাছাকাছি চলে আসবে এবং নতুন অণু প্রবেশের জায়গা সৃষ্টি হবে৷ পানির ক্ষেত্রে কি এই ঘটনা তেমন ঘটে? না, ঘটেনা। এজন্য পানি অসংকোচনযোগ্য প্রবাহীর শ্রেণীতে যায়। আর এই কারণেই পানির ঘনত্ব এবং স্তরায়ণের উপর চাপের তেমন একটা প্রভাব দেখা যায় না।
কিন্তু তাপমাত্রা এই স্তরায়ণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধরি, দুটি পানির স্তরের লবণাক্ততা এবং বাকিসব প্যারামিটার একই। স্বাভাবিকভাবেই যে অংশের তাপমাত্রা যত বেশি সে অংশের আয়তন তত বেশি হবে (তাপমাত্রা বাড়লে প্রবাহীর অনুগুলির ছোটাছুটি বাড়ে, ফলে বেশি জায়গা দখল করে), ঘনত্ব কম হবে। কিন্তু ভর একই। তাহলে ঐ স্তরের ওজন (mg) একই ভরের অপর একটি পানির স্তরের ওজনের সনান হলেও আয়তন বেশি হওয়ার দরুণ প্লবতা (Vρg) অপর স্তর অপেক্ষা বেশি হবে। আর আমরা কী জানি? প্লবতা বেশি হলে সে তত বেশি উপরে ঠেলে উঠবে। তাহলে বিষয় কেমন দাঁড়ালো?
বেশি ঘনত্ব কিন্তু অনেক বেশি তাপমাত্রা → সবার উপরে
কম ঘনত্ব কিন্তু তুলনামূলক কম তাপমাত্রা → মাঝে
বেশি ঘনত্ব এবং কম তাপমাত্রা → সবার নিচে
এভাবে পদার্থবিজ্ঞানের ৯ম-১০ম শ্রেণীতে পঠিত নীতি মেনে একটা জলাধারের পানি এমন অবস্থায় থাকতে পারে যেনো মনে হয় এই পানি একে অপরের সাথে মিশবেই না। তবে কাহিনী হলো, পানি কিন্তু ঠিকই একে অপরের সাথে মিশে। সে যতই স্তরায়ণ ঘটুক না কেনো, কোনে অদৃশ্য অন্তরাল সৃষ্টি হবেনা যে পানি মিশবেই না একদম। কোনো জলাধারের পানি ধরুন এরকম স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে, যদি কোনোরকম বাহ্যিক প্রভাব নাও থাকে তবু দেখা যাবে উচ্চ ঘনত্বের স্তর থেকে নিন্ম ঘনত্বের স্তরে পানির ব্যাপন হওয়া শুরু হবে। বাল্যকালেই আমাদের ব্যাপন সম্পর্কে পড়ানো হয়। এই ব্যাপন তুলনামূলক ধীরে হলেও ঘনত্বের পার্থক্য বজায় থাকবে যতক্ষণ, ব্যপনের মাধ্যমে পানিও মিশবে ততক্ষণ। ঘনত্ব একবার সমান হয়ে গেলে তখন সব স্তরের তাপমাত্রা, উপাদান সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, তখন আর স্তর স্তর বোঝাও যাবেনা। কিন্তু ওই যে বললাম বাহ্যিক প্রভাব না থাকলে! বাহ্যিক প্রভাব থাকবেনা তাই কি কখনো হয়? প্রকৃতি কি এতই সহজ সরল?
i) তাপমাত্রা: জলাধারের উপরিতল সূর্যের আলোর দিকে উন্মুক্ত থাকে বিধায় উপরিস্তরের তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি হয়। ফলে উপরিস্তরের আয়তনও বেশি হয়, ঘনত্ব কমে যায়। ফলে উপরিস্তরের সাথে এর পরবর্তী স্তরের ঘনত্বের পার্থক্য বজায় থাকে, স্তরায়ণও বজায় থাকে।
ii) বায়ুপ্রবাহ: ক্রমাগত বায়ুপ্রবাহের ফলে উপরিতলে স্রোত-ঢেউ বজায় থাকে যা পানির বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি করে। উপরিস্তরের দ্রুত বাষ্পায়নের ফলে পানির পরিমাণ কমে যায় এবং উক্ত স্তরের ঘনত্ব লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়।
আবার বায়ুপ্রবাহ উপরিতলে যে স্রোতের সৃষ্টি করে তার ফলে উপরিস্তরে থাকা গরম পানি সরে যায় এবং নিচের স্তরের ঠান্ডা ঘন পানি সেই জায়গা পূরণ করে। একে বলে আপওয়েলিং (Upwelling)। এই আপওয়েলিং এর দরূণ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পানির মধ্যে মিশ্রণ আরও দ্রুত ঘটতে পারে।
তাহলে মোদ্দাকথা দাঁড়ালো ঠিকমতো বায়ুপ্রবাহ না থাকলে শুধু তাপমাত্রার দরুণ কোনো জলাধারে যেমন স্তরায়ণ বজায় থাকতে দেখা যায়, ঠিক তেমন বায়ুপ্রবাহের দরুণ সৃষ্ট স্রোত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পানির মিশ্রণ ঘটায়। অর্থাৎ, পানির স্তরায়ণের ক্ষেত্রে কোনো অদৃশ্য প্রাচীরের কোনো ভূমিকাই নাই, আছে বহুল প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের নীতি!!
এবার ফিরে আসা যাক ভূমধ্যসাগর-আটলান্টিকের গল্পে যেখানে জনাব ইব্রাহীম দাবী করেছিলেন এদের পানি কখনোই মিশে না, যে যার মতো প্রবাহিত হয়ে দুই লেয়ারে পৃথক হয়ে থাকে সর্বদা। আদতে এই দাবীকে গুজব কিংবা ভুয়া আখ্যা দেওয়া যায়। আটলান্টিকের পানির উপরিস্তর উচ্চ তাপমাত্রার কারণে হালকা এবং কম ঘনত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পানি ভূমধ্যসাগরের পৃষ্ঠতলে প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আপওয়েলিং এর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরের পানির সাথে প্রশান্ত মহাসাগরের পানির মিশ্রণ ঘটে। একইসময়ে ভূমধ্যসাগরের নিন্মস্তরের পানি গিব্রাল্টারের পানিপথ দিয়ে দ্রুতবেগে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। এবং ভূমধ্যসাগরের পানি ও আটলান্টিকের পানি আলাদা আলাদা খালি চোখে বোঝা যায়। কিন্তু এর মানে এদের পানি মিশেই না এটা ভূল ধারণা একদম, একই সাথে একই সময়ে উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে দুই সমুদ্রের পানির মধ্যে মিশ্রণ চলতে থাকে। সেই মিশ্রণ তুলনামূলক ধীরগতির হওয়ায় মনে হতে পারে পানি কোনো অদৃশ্য অন্তরক প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা আছে যা বাস্তবে সত্য নয়। ধন্যবাদ।
References:
1) Wikipedia, Stratification (water)
2) BBC Science Focus, Is it true that the Pacific and Atlantic Oceans don’t mix?
3) Live Science, Do the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean mix?
4) Wikipedia, Mediterranean outflow