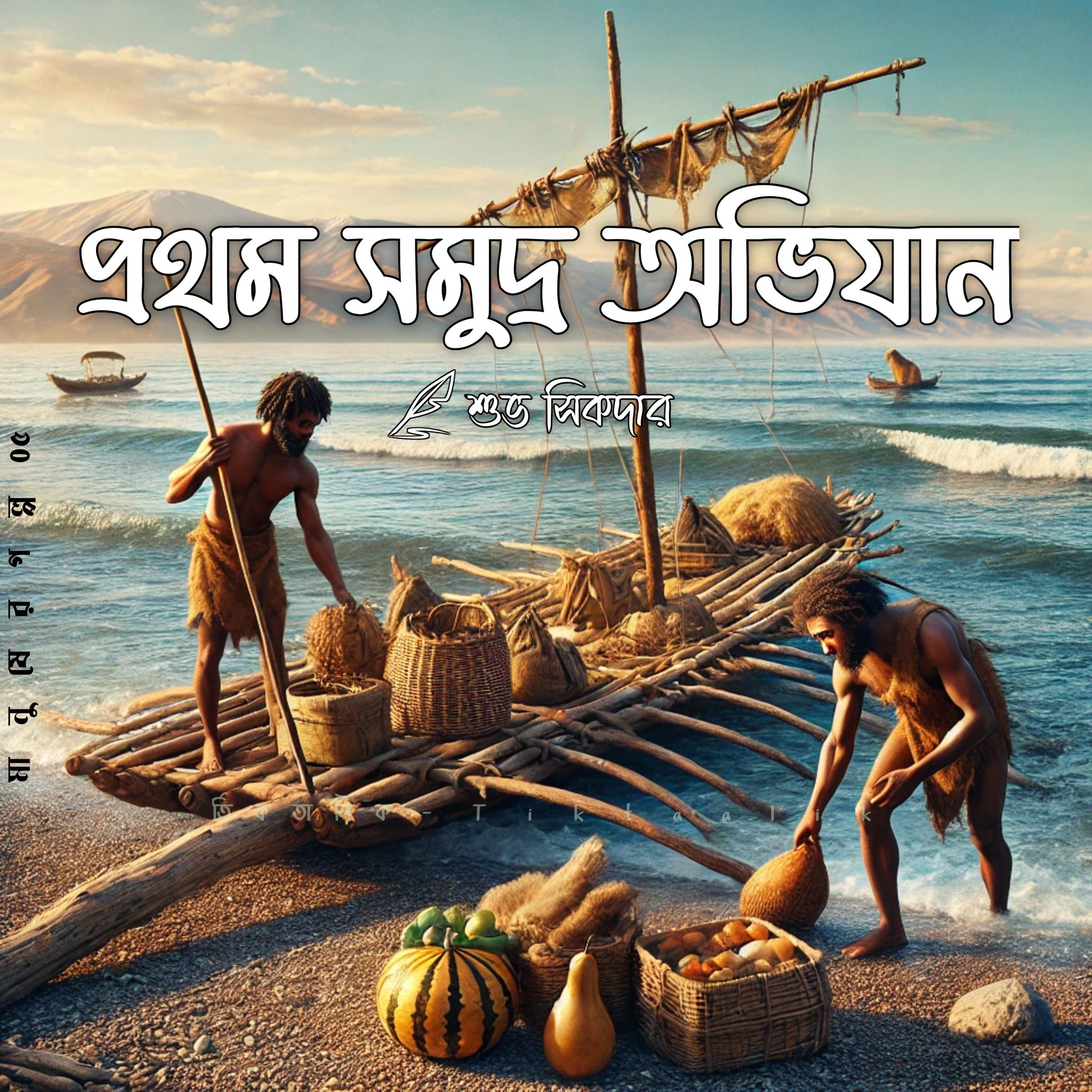ইতিহাসের দিনপঞ্জিটা বের করে একবার মেলে দেখার দিন আজ। মাত্র ৪৬০০ বছর আগেকার সময়রেখায় নজর দিলে আমরা দেখবো পিরামিড। প্রথম লিখিত নথিপত্রের পড়তে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ৫৪০০ বছর আগে। ৮০০০ বছর পেছনে গেলে আমরা দেখা পাবো নৌকার। এখন অব্দি খুঁজে পাওয়া মানবজাতির সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকর্ম কী জানেন? একটা সিংহমানব। আর এই সিংহমানবটি বানানো হয় ৩৪,০০০ বছর আগে, স্টাডেলের সিংহ।
আবিষ্কারের নেশায় স্যাপিয়েন্স যখন আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে পড়লো অস্ট্রেলীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে, সেই সময়টা উপরে উল্লিখিত সময়কাল অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি প্রাচীন, স্যাপিয়েন্সের প্রথম সমুদ্র অভিযান আজ থেকে প্রায় ৬৫০০০ বছর আগে হয়েছিলো। আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া, সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু অত আগে সমুদ্রপথ তারা পাড়ি দিয়েছিল কিভাবে?
১৯৫৫ সাল। নেদারল্যান্ডসের পেস গ্রামে চলছিলো A28 মোটরওয়ের খনন কার্যক্রম। সেখানেই খুঁজে পাওয়া যায় গাছের গুঁড়ির মতো কিছু একটা। ইউনিভার্সিটি অব গ্রোনিংজেনের বিজ্ঞানীরা কার্বন ডেটিং করে গুঁড়িটির বয়স নির্ণয় করতে সক্ষম হন। প্রায় ৮ হাজার বছর প্রাচীন এটা। নিওথিলিক পাথর যুগে নৌকা হিসেবে ব্যবহার করা হতো এটিকে, বিশেষজ্ঞরা এটার নাম দেন পেস ক্যানয়। কিন্তু এটা সামান্য একটা কাঠই, ভেলার ন্যায় ছোট একটা কাঠামো, ডিঙি নৌকার থেকেও ছোটো। এর উপর ভর করে সর্বোচ্চ ছোটখাটো কোনো খাল পাড়ি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমুদ্রের বেলায়? ভারত মহাসাগরে এই ভেলা নিয়ে অভিযানে নামলে তো সলিল সমাধি নিশ্চিত! ওরকম কিছু একটা নিয়ে কিভাবে কেউ এক্সপেডিশনে বেরিয়ে যেতে পারে?
এবার একটু হিসেবনিকেশ করা যাক। তখনকার গ্লেশিয়াল যুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেক নিচে ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর নিউগিনি তখন স্থলপথে সংযুক্ত ছিল, প্রায় ১৫০ কিলোমিটার সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হতো। পথ কম, কিন্তু একবারে কম না। এই পথ পাড়ি দেওয়ার সময় প্রথম বাঁধাটা আসবে ঢেউয়ের তরফ থেকে। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ খুব সহজেই অভিযাত্রীর ভেলা ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে সম্ভবত আমাদের পূর্বজরা অপেক্ষা করেছিলেন শান্ত আবহাওয়ার জন্য, কারণ ঝড়ো বাতাস সমুদ্রকে আরও উত্তাল করে তোলে যেটা যাত্রীদের জন্য অসুবিধা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এজন্য অপেক্ষা করে, ধৈর্য্য ধরে শান্ত বাতাসে যাত্রা করাটাই বেশি সুবিধাজনক তাদের জন্য। তাছাড়া ভাসমান ভেলার গঠন এমন ছিল, যেনো বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ করে সেগুলো পুরোপুরি ডুবে না যায়। এই যাত্রায় দ্বিতীয় বাঁধা হিসেবে সামনে আসে রসদ। পুচকে ওই ভেলা তথা নৌকায় একসাথে খুব বেশি রসদ নেওয়ার সুযোগ ছিলো না। সুতরাং, তাদের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা ছিল স্থানীয় সম্পদ। সমুদ্র এবং উপকূল থেকে মাছ কিংবা শামুকের মতো সহজলভ্য খাবার সংগ্রহ করে নিতে হতো তাদের, এটাই ছিলো এই সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। পানযোগ্য পানি বহন করা কঠিন ছিলো। স্থলপথে থামার সময় পানির খোঁজ করাই ছিলো বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত। একসাথে পুরো সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়া কখনোই সম্ভবপর ছিলো না। যাত্রা শুরু করতে হতো উপকূল বরাবর, উপকূলেই থেমে থেমে বিশ্রাম এবং রসদ সংগ্রহের কাজ করতে হতো, উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোই ছিল পথিকদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল।
তৃতীয় বাঁধা ছিলো সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটা উপায় জানা ছিল তাদের।
→ সূর্যের অবস্থান দেখে পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত বোঝা ছিলো খুবই সাধারণ বিষয়। সকালে সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে যাত্রার দিক ঠিক করা হতো। কিন্তু রাতের বেলায়? তখন তো আকাশে সূর্য থাকেনা! এসময় কাজে আসে আকাশের তারামণ্ডল। এই তারামণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে দিক নির্ণয় করা ছিলো আরেকটি চিরন্তন উপায়।
→ ঋতু বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাতাসের দিক দেখেই বলে দিতে পারতেন কোনটা কোন দিক।
→ সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা দেখেও তারা বুঝে ফেলতেন যে জায়গাটা উপকূলের কাছাকাছি নাকি গভীর সমুদ্রে!
→ উপকূলীয় অঞ্চলের পাখিরা গোধূলি হলেই উড়াল দেয় স্থলপথের দিকে। সেটা দেখেও আপনি দিক সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। কিছু জলজ প্রাণীর গতিবিধি দেখেও সমুদ্রের গভীরতা আন্দাজ করা যেত।
→ গভীর সমুদ্রের পানি হয় নীল। উপকূলে গেলেই সেটা হালকা সবুজ কিংবা বাদামি হতে শুরু করে। আবার স্থলপথের কাছাকাছি গেলে বাতাসে গাছপালা এবং মাটির ঘ্রাণও টের পাওয়া যেতো।
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম থেকে পাওয়া বিদ্যা আর অভিজ্ঞতায় সেপিয়েন্সরা দিক নির্ণয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, একটা প্রশ্ন মনে থেকেই যায়। এতো ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের কি এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো? ভালো করে চিন্তা করলে কিছু অবশ্যম্ভাবী কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।
প্রথমত, আফ্রিকায় খাদ্যের ওপর চাপ বেড়েই চলছিল। একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা। সাথে আবার যোগ হয়েছিল, স্থান সংকুলানের সমস্যা। নতুন জমি খুঁজে বের করতেই হতো।
দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে বিচরণ করা তখন আমরাই একমাত্র মানবপ্রজাতি ছিলাম না। এশিয়ায় হোমো ইরেক্টাস ছিল। ইউরোপে ছিল নিয়ান্ডারথাল। ওদের সাথেও প্রতিযোগিতায় আমাদের শামিল হতে হচ্ছিলো। নিজেদের মধ্যে মারামারি, যুদ্ধ, গণহত্যার মতো বিষয়গুলি অস্বাভাবিক ছিল না। ফলে নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল খোঁজাটাও জরুরি হয়ে পড়েছিলো।
তৃতীয়ত, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছু অঞ্চল শুষ্ক হয়ে পড়ছিল। অস্ট্রেলিয়ার মতো উষ্ণ এবং আর্দ্র হতে পারতো একদম জুতসই গন্তব্য।
চতুর্থত, কৌতুহল। নিজেদের ছোট্ট এলাকার বাইরে বিশাল দুনিয়া জানার কৌতুহল। এই কৌতুহল আর নতুন আবিষ্কারের নেশাই স্যাপিয়েন্সকে এতদূর নিয়ে এসেছে। কৌতুহল না থাকলে হয়তো আমরা ছোট্ট একটা এলাকাতেই আবদ্ধ থেকে যেতাম।
আজকের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা। হিস্টরিক্যাল সায়েন্সের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার পথে একটা বড় সমস্যা হলো- আমরা কেউই অতীতে গিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারিনা আসলেই কী ঘটেছিলো। আমাদের নির্ভর করতে হয় বর্তমানে পাওয়া টুকরো টুকরো এভিডেন্সের উপরে। সেই প্রমাণ, অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহ মাথায় রেখে যুক্তি সাজালে মোটামুটি একটা ইতিহাস আমাদের সামনে চলে আসে। এভিডেন্স অনেক কম হলে একাধিক মতবাদ দেখা যায়, আবার কোনো মতবাদের পক্ষে অনেক বেশি এভিডেন্স পাওয়া গেলে তখন সেটা হয় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, সেটাই ঘটেছিলো এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ঠিক তেমনই এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, এতটা কিভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে মানুষ তখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলো?
যুক্তির প্রথম কিস্তিতে আসে- প্রয়োজনীয়তা। উপরে আফ্রিকায় খাদ্যের অভাব, জমির অভাব, আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চল খুঁজে পাওয়ার তাগিদ, অন্যদের থেকে বাঁচতে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখেছি আমরা।
যুক্তির দ্বিতীয় কিস্তিতে আসে- পরিবর্তনশীল ভৌগলিক গঠন। সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার কোন দরকারই পড়তো না যদি কিনা ২০০ মিলিয়ন বছর আগে প্যানজিয়া সুপার কন্টিনেন্ট ভেঙে না যেতো। এটা না ভাঙলে স্থলপথেই উপরে উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে ফেলতে পারতো স্যাপিয়েন্সরা। কিন্তু মানুষের আবির্ভাবের বহু আগেই, জুরাসিক যুগের শুরুতেই অবিভক্ত পৃথিবী ভাঙতে শুরু করে। এই ভাঙনের পর এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া কখনোই সরাসরি যুক্ত ছিলো না। এমনকি বরফযুগেও এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ার দিকে যেতে হলে সমুদ্রপাড়ি দেওয়া অবধারিত ছিলোই।
যুক্তির তৃতীয় কিস্তিতে আসে- প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আধুনিক মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায় প্রায় ৬৫০০০ বছর আগে। মাদজবিতব অঞ্চলে পাওয়া প্রাচীন কিছু হাতিয়ার তো সেই সাক্ষ্যই দেয়। লেক মুঙ্গোতে পাওয়া মুঙ্গো লেডি এবং মুঙ্গো ম্যানের জীবাশ্ম প্রায় ৪২০০০ বছর পুরনো। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মুঙ্গো লেডিকে আগুনে পুড়ানো হয়েছিলো। মানবজাতির ইতিহাসে এখনো অব্দি পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন শবাদাহ করার প্রমাণ এটাই। অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া এসব প্রত্যক্ষ এভিডেন্স আমাদের নিশ্চিত করে স্যাপিয়েন্স বহু বহু আগেই সমুদ্রপাড়িয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া পৌছেছিলো, কারণ জলপথ ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের নিকট ছিলোনা।
এবার একটা দৃশ্যপট কল্পনা করুন। ভিটেমাটি ছেড়ে একদল মানুষ নৌকায় চড়ে বেরিয়ে পড়ছে। দুর্গম জলপথ পেরিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। রোমাঞ্চকর অভিযান সম্ভবত এটাকেই বলে, রোমাঞ্চ এখানেই সর্বোচ্চ চূড়া ছুঁয়ে যায়। রবি ঠাকুর এমন মুহূর্তের জন্যই বোধহয় লিখেছিলেন,
“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো।”
লেখক: শুভ শিকদার, পদার্থবিজ্ঞান, সেলজুক বিশ্ববিদ্যালয়, কোনিয়া, তুরস্ক।
সম্পাদনা: তিকতালিক-Tiktaalik
কপিরাইট: লেখক, তিকতালিক-Tiktaalik